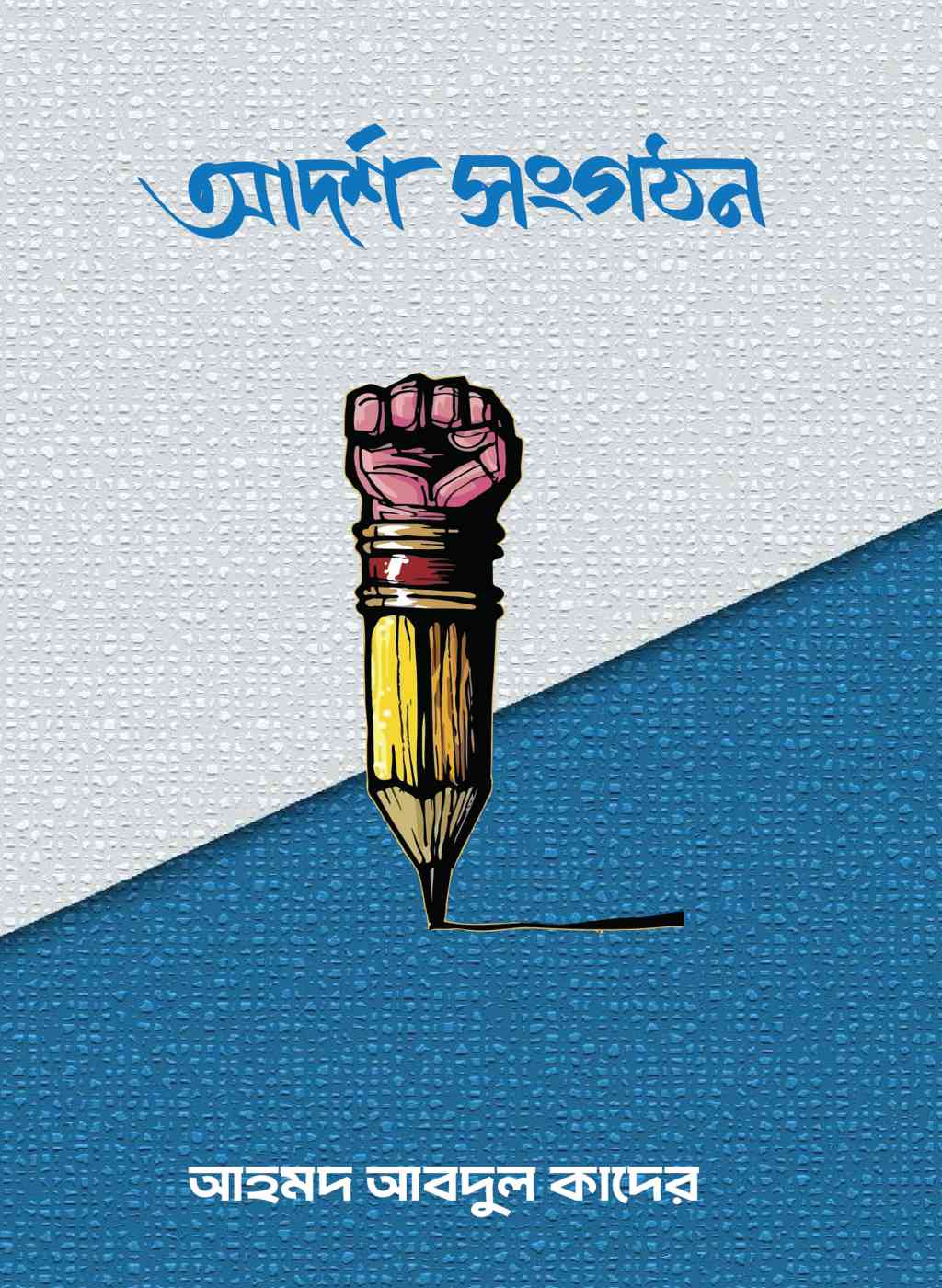আদর্শ সংগঠন
বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৭
- লেখক: ড. আহমদ আবদুল কাদের
- প্রকাশক: ছাত্র মজলিস প্রকাশনা বিভাগ
আদর্শ সংগঠন
ড. আহমদ আবদুল কাদের
১ম সংস্করণ ও প্রকাশ
রবিউল আউয়াল-১৪৪৭ ভাদ্র-১৪৩২ সেপ্টেম্বর-২০২৫
প্রকাশনায়
আইসিএম পাবলিকেশন্স ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৭১১-৩১৮৩২৭
মূল্য:
১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র
আদর্শ সংগঠন
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
আদর্শ সংগঠন
ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আন্দোলন প্রয়োজন। আবার ইসলামী আন্দোলনের জন্য ইসলামী সংগঠন প্রয়োজন। তাই ইসলামী সংগঠন বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনকারী সংগঠনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অবহিত থাকা অত্যাবশ্যক। এ প্রয়োজন সামনে রেখেই বর্তমান আলোচনা।
সংগঠন
সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে কোন নেতৃত্বের অধীনে একাধিক ব্যক্তির একত্রিত হওয়া বা সংঘবদ্ধ হওয়াকে সংগঠন বলে।
সংগঠনের উপাদান
একটি সংগঠনের কতিপয় উপাদান থাকে, যার ভিত্তিতে সংগঠন গঠিত ও পরিচালিত হয়। এসব উপাদানের মধ্যে চারটি হচ্ছে অত্যন্ত মৌলিক। এগুলো হলো: ১. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ২. নেতৃত্ব, ৩. সদস্যমণ্ডলী ও ৪. কর্মসূচি।
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: যে কোন সংগঠন গড়ে তোলার পেছনে কোন না কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া কোন সংগঠনই হতে পারে না। উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্যই সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সংগঠনের উদ্দেশ্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী হতে পারে। উদ্দেশ্য স্থায়ীও হতে পারে। অস্থায়ী বা সাময়িকও হতে পারে। কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য ইহলৌকিক হতে পারে আবার পারলৌকিকও হতে পারে। বস্তুগত উদ্দেশ্যে সংগঠন কায়েম হতে পারে আবার আধ্যাত্মিক-নৈতিক উদ্দেশ্যেও সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। বস্তুত ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠতে পারে।
নেতৃত্ব: নেতৃত্ব হচ্ছে সংগঠনের প্রাথমিক উপাদান। নেতৃত্ব ছাড়া কোন সংগঠন হয় না। একটি সংগঠন গড়ে তোলা ও পরিচালিত হওয়ার জন্য সংগঠনের বিভিন্ন স্তরেই নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে শুরু করে নিম্নতম শাখা পর্যন্ত সর্বত্রই নেতৃত্ব অপরিহার্য। সংগঠনের জন্য নেতৃত্ব লাগবেই।
সদস্যমণ্ডলী: কতিপয় লোকের সম্মিলনেই একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। কোন লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যারা একত্রিত হয় তারাই হচ্ছে সংগঠনের সদস্য। যাদের নিয়ে সংগঠন করা হয় তারাই সংগঠনের সদস্যমণ্ডলী। সদস্য না থাকলে কোন সংগঠনই গড়ে উঠবে না। তাই সদস্যমণ্ডলী হচ্ছে সংগঠনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐকমত্য পোষণকারী কতিপয় লোক একত্রিত হওয়ার মাধ্যমেই সংগঠনের গোড়াপত্তন হয়। নেতৃত্বও সদস্যমণ্ডলীর মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে।
কর্মসূচি: লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে সমস্ত মৌলিক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় তাই কর্মসূচি। প্রত্যেকটি সংগঠনেরই সুনির্দিষ্ট কতিপয় কর্মসূচি থাকে। কর্মসূচি ছাড়া কোন সংগঠনই তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। এজন্য কর্মসূচি সংগঠনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। কর্মসূচি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। স্থায়ী ও অস্থায়ী। কতিপয় কর্মসূচি এমন আছে যা সংগঠনের স্থায়ী কার্যক্রম বলে বিবেচিত হয়। সেগুলো হচ্ছে স্থায়ী কর্মসূচি। কিন্তু কর্মসূচি অবস্থা, পরিস্থিতি ও সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে গ্রহণ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে, অস্থায়ী কর্মসূচি। যাই হোক, প্রত্যেকটি সংগঠনের কিছু না কিছুই কর্মসূচি থাকবেই। কর্মসূচি ছাড়া সংগঠন চলবে না।
ইসলামী সংগঠন
ইসলামসম্মত কোন উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে ইসলামী সংগঠন বলা হয়। অর্থাৎ একটি সংগঠন ইসলামী বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য সংগঠনটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামসম্মত হওয়া চাই। আর ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সংগঠনটি পরিচালিত হয়।
ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন
দ্বীন কায়েম তথা ইসলামী আন্দোলন করার জন্য যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে ইকামতে দ্বীনের সংগঠন বা ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন বলা হয়।
ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
১. আংশিক নয় পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েম তথা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ বা খেলাফত ব্যবস্থা কায়েমই সংগঠনের লক্ষ্য। আর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।
২. সংগঠনের যাবতীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি এবং পলিসি নির্ধারণ কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হতে হবে।
৩. সংগঠনের নেতৃত্বে থাকবেন মুত্তাকী, আদেল ও দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কে যারা ইলম রাখেন এবং যারা নিজেদের জীবনে দ্বীনি বিধি-বিধান মেনে চলেন, তারাই নেতৃত্ব দেবেন।
৪. সংগঠনের কর্মীদের দ্বীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে সংগঠন কায়েম হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েমের জন্য সে সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে দ্বীনি প্রশিক্ষণ ও তরবিয়াতের ব্যবস্থা অপরিহার্য।
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
মৌলিক চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনে থাকা প্রয়োজন। তা না হলে সঠিকভাবে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা ঐ সংগঠনের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেগুলো প্রধানত নিম্নরূপ-
১. নির্ভেজাল ইসলামের অনুসরণ ও প্রচার: বর্তমান ইসলামের কথা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা উচ্চারিত হয়। অনেকে ইসলামের ভুল বা বিভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অনেকে পাশ্চাত্য মতবাদের সঙ্গে ইসলামকে মিশ্রিত করে ফেলেছেন। অনেকে পতন-যুগের ইসলামের ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। বস্তুত কুরআন-সুন্নাহ, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ইসলামের নির্ভরযোগ্য ও সঠিক ব্যাখ্যা। ইসলামের সে আদি ও নির্ভেজাল ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করতে হবে। তার আলোকেই আন্দোলন চালাতে হবে।
২. দ্বীনি ঐতিহ্য সংরক্ষণ: বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে দ্বীন ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। ঐতিহ্যকে অস্বীকার বা বিনষ্ট করা যাবে না। তাকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নয় বরং অতীত দ্বীনি ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়েই ভবিষ্যত নির্মাণ করার প্রয়াস চালাতে হবে।
৩. হকপন্থী আলেমগণের অংশগ্রহণ, সমর্থন ও নেতৃত্ব থাকা: একটি ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনে অবশ্যই সমাজের হক ও ন্যায়পন্থী আলেম-ওলামাগণের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। তাদের সমর্থন ও সক্রিয় নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না।
৪. সার্বজনীনতা: দ্বীন কায়েমের সংগঠনকে বিশেষ কোন দলবাদী, গোষ্ঠীবাদী, ফেরকাবাজিসহ যাববতীয় সঙ্কীর্ণ চিন্তার উর্ধ্বে থাকতে হবে। সংগঠন হবে ইসলামের সার্বজনীন ভাবধারায় পুষ্ট।
৫. ঐক্যকামী: দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগঠনকে মুসলমান ও ইসলামী শক্তিসমূহের মধ্যে ঐক্যকামী ও প্রয়াসী হতে হবে। সংগঠন উম্মতের মধ্যে ও ইসলামী শক্তির মধ্যে বিভক্তির জন্য কাজ করবে না; বরং উম্মাহর ঐক্য ও ইসলামী শক্তির ঐক্যের লক্ষ্যে কাজ করবে।
৬. সংগঠন হবে উপায়, লক্ষ্য নয়: একটি সংগঠন করার উদ্দেশ্য হবে দ্বীন কায়েমের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা। সংগঠন নিজেই কোন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যম মাত্র। মনে রাখা দরকার সংগঠনের স্বার্থের চেয়ে আন্দোলনের স্বার্থ অনেক বড়। আবার আন্দোলনের চেয়ে ইসলামের স্বার্থ বড়।
৭. আপোষহীনতা: সংগঠন হবে ইসলামী নীতি, আদর্শ ও আন্দোলনের স্বার্থের প্রশ্নে আপোষহীন। একটি ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন ইসলামী নীতিমালা সংরক্ষণের প্রশ্নে কোন অবস্থায়ই আপোষ করতে পারে না। যেন-তেন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। দ্বীন কায়েম করাই উদ্দেশ্য। জাহেলী ও তাগুতী ব্যবস্থা উৎখাত করা উদ্দেশ্য। তাই দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করে জাহেলী ব্যবস্থা ও তাগুতের সাথে আপোষ করে দ্বীন কায়েম করা যায় না। আবার দল বা ব্যক্তির স্বার্থেও আন্দোলনের স্বার্থ বিলিয়ে দেয়া যায় না। তাই দ্বীনি সংগঠন হবে নীতির প্রশ্নে আপোষহীন।
৮. মজলুম-মুস্তাদআফীনের মুখপাত্র: ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য সমাজের নিগৃহীত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তি। তাই দ্বীন কায়েমের সংগঠনকে সমাজের মজলুম নিগৃহীত, বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হতে হবে। তাদের মূখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। দ্বীনি সংগঠন হবে মজলুম শ্রেণীর সংগঠন। এ হবে গরিব-দুঃখী ব্যক্তি ও মানুষের আশ্রয়।
৯. সমন্বয়ধর্মী: ইকামতে দ্বীনের সংগঠন হবে সমন্বয়ধর্মী সংগঠন। এখানে আলেম-ওলামা ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর সমন্বয় ঘটবে। পুরাতন ঐতিহ্যপন্থী ও আধুনিক যুগ সচেতনদের এখানে মিলন ঘটবে। সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন দ্বীনি ধারার সুন্দর সমন্বয় থাকবে ইকামতে দ্বীনের সংগঠনে।
১০. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী: ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে আপোষ করবে না, নমনীয় হবে না। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে বিশ্ব কুফর ও বৈশ্বিক তাগুতের প্রতিভূ। তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা, তাদের সঙ্গে আপোষ না করা, দ্বীনি সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এসব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিতেই একটি সংগঠন যথার্থ পথে অগ্রসর হতে পারে। অন্যথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিতে বাধ্য।
সংগঠনের গুরুত্ব
ইসলামে সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্ব অনেক বেশি। ঐক্যবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতি কুরআন-সুন্নাহ অত্যন্ত তাগিদ করেছে। তাছাড়া ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকেও সংগঠনের অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো:
সংঘবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতার শরয়ী গুরুত্ব
১. ইসলাম মুসলমানদের সমাজবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ জীবন চায়। বিক্ষিপ্ত হতে নিষেধ করে। পবিত্র কুরআন দ্বীনের রজ্জুকে সবাই মিলে আঁকড়ে ধরতে বলেছে। অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছে।
واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
‘তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর অনৈক্য সৃষ্টি করো না।’ (সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১০৩)
উপরোক্ত আয়াত থেকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধতার অপরিহার্যতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
২. অস্থায়ী অবস্থায়ও সংঘবদ্ধতা অপরিহার্য। সংঘবদ্ধতার গুরুত্ব এত বেশি যে, সফরের মতো অস্থায়ী অবস্থায়ও সংবদ্ধ থাকার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে। বন-জঙ্গলে বা মরুভূমিতে তিনজন লোক অবস্থান করলেও সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা অপরিহার্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট:
إذَا كَانَ ثَلَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمُ.
‘সফরে এক সঙ্গে তিনজন লোক থাকলে তাদের মধ্য থেকে যেন একজনকে আমীর করে নেয়।’ (আবু দাউদ)
অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে:
لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ يَكُونُ بِفُلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.
‘তিনজন লোকও যখন কোন বিজন এলাকায় বাস করবে তখনও তাদের মধ্যে কাউকে আমীর না বানিয়ে বাস করা জায়েয নয়।’ (মুসনাদে আহমদ)
অন্য একটি হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:
مَا مِنْ ثَلَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بُدَّ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحُونَ عليهم الشيطان فعليك بالجماعةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِية.
‘কোন জঙ্গলে বা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তারা যদি তখন (জামাতবদ্ধভাবে) নামায কায়েমের ব্যবস্থা না করে তবে শয়তান তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব জামাতবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য। কেননা পাল হতে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে নেকড়ে সহজেই খেয়ে ফেলে।’ (আবু দাউদ)
যেখানে সফরের মতো অস্থায়ী অবস্থায়ও সংঘবদ্ধ থাকা জরুরি সেখানে স্থায়ীভাবে বাসকারী অথবা স্থায়ী কোন লক্ষ্যে কর্মরত জনগোষ্ঠীর জন্য সংঘবদ্ধতা যে আরো কত গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।
৩. সংঘবদ্ধতা তথা মুসলমান জামাত ও সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের কাজ। একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
مک امركُم بِخَمْسِ بِالْجَمَاعَةِ والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله.
আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি: ১. জামাতবদ্ধ তথা সংঘবদ্ধ থাকা, ২. আদেশ শ্রবণ, ৩. আনুগত্য, ৪. হিজরত, ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)
উপরোক্ত হাদীসটিতে দ্বীনি আন্দোলন তথা ইসলামী আন্দোলনের মৌল কর্মসূচিগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব কর্মসূচির প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে জামাতবদ্ধতা বা সংগঠিত হওয়া ও সংগঠিত থাকার কথা। এ হাদীস থেকে একথাও বুঝা যায় যে, দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ‘জিহাদ’ সম্পাদন করতে হলে প্রথমেই সংগঠন, আদেশ শ্রবণ, আনুগত্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছাড়া হিজরত-জিহাদ কিছুই সম্ভব নয়। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)
৪. সংঘবদ্ধতা ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন করা সম্ভব নয়: ইসলামে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম সামষ্টিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হয় সেগুলো একা একা কায়েম করা সম্ভব নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়ে ইসলাম যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই সরকার ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজন পূরণ সংঘবদ্ধতা ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনকে সামনে রেখেই হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) ঘোষণা করেছেন:
لا اسلام إِلَّا بِجَمَاعَةِ.
‘জামাত তথা সংগঠন-সংঘবদ্ধতা ছাড়া ইসলাম পালন সম্ভব নয়।’
অতএব দ্বীন যথাযথভাবে পালন ও বাস্তবায়িত করতে হলে সংগঠিত হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।
৫. মুসলিম সমাজের মধ্যে সর্বদাই একটি কল্যাণবাহী দলের উপস্থিতি প্রয়োজন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাধারণভাবে মুসলিম মিল্লাতকে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার উম্মতের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব বিশেষভাবে পালন করার জন্য একটি জনগোষ্ঠী বা দলের উপস্থিতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে যখন মুসলিম উম্মত সংঘবদ্ধভাবে এ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়বে, তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বিক্ষিপ্ততা দেখা দেবে তখন কল্যাণের পথে মানুষকে ডাকা, সৎ কাজের নির্দেম দান করা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার জন্য একটি দল, সংগঠন, সংস্থা অবশ্যই গড়ে উঠতে হবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:
وَلَتَكُن مِنْكُمُ اللهُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهونَ عَنِ الْمُنكَرِ.
‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎ কাজে আদেশ দিবে, অসৎ কাজে বাধা দিবে।’ (সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১০৪)
উপরোক্ত আয়াত উম্মতে মুসলিমার মধ্য থেকে একটি সুসংগঠিত জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠাকে অপরিহার্য করে। যারা কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎ কাজে আদেশ দিবে, অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখবে তারা নিশ্চয়ই অসংগঠিত, অসংঘবদ্ধ হলে চলবে না। তাদেরকে অবশ্যই সংগঠিত হতে হবে, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।
৬. ইসলামের সামষ্টিক প্রকৃতির ইবাদতগুলোও সংগঠিত হওয়া ও থাকার প্রয়োজনীয়তাকে সুস্পষ্ট করে তোলে ইসলাম যে সমস্ত ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে ফরয-ওয়াজিব করেছে সেগুলোও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামষ্টিক চরিত্রের। সংঘবদ্ধভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে হয়। যেমন জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমার নামায, ঈদের নামায, জানাযার নামায, হজ্জের অনুষ্ঠান ইত্যাদি। জুমা, ঈদ, জানাযা ইত্যাদি তো জামাত ছাড়া সম্পাদনই করা যায় না। এসব থেকে কি বুঝা যায়? সংঘবদ্ধতার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতাই কি ফুটে ওঠে না? মুসলমানদের ফরয ইবাদত-বন্দেগীও যদি জামাত ছাড়া সম্পাদন না করা যায় বা জামাত ছাড়া এসব পূর্ণতা লাভ না করে তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত থাকার গুরুত্ব তো সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অতএব মুসলমানদের যে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত জীবন যাপন করতে হবে সামষ্টিক চরিত্রের ইবাদতগুলো থেকে তার শিক্ষা ও নমুনা পাওয়া যায়।
৭. মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ ও দলাদলি করা এবং জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে: এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।
পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছে এবং দলাদলি ও মতবিরোধ করতে নিষেধ করেছে।
واعتصموا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
‘সবাই মিলে আল্লাহ তাআলার রজ্জু আঁকড়ে ধর। বিভেদ সৃষ্টি করো না-বিচ্ছিন্ন হইও না।’ (সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১০৩)
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
‘স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিধান আসার পরও যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, মতবিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করেছে তোমরা তাদের মত হইও না। যারা এরূপ করবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।’ (সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১০৫)
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি এত বড় অপরাধ যে প্রয়োজনে তলোয়ার দিয়েও তার প্রতিবিধান করতে হবে। হাদীসে আছে:
فَمَنْ أَرَادَ أن سفير أمر هذه الأمة وَهِيَ جَمِيعَ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنَا مَنْ كَانَ.
‘সুতরাং যে ব্যক্তি এ উম্মতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে তলোয়ার দ্বারা তাকে শায়েস্তা কর, চাই সে যে হোক না কেন।’ (মুসলিম)
অন্য এক আয়াতে দ্বীনের মধ্যে বিরোধ-বিভেদ সৃষ্টি ও দলাদলি করার সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা হয়েছে:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا تَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
‘যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড করে নিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে অবশ্যই তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।’ (সূরা আনআম: আয়াত ১৫৯)
যারা মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةِ فَمَاتَ مَنَةً جَاهِلِيَّةً.
যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার মৃত জাহেলিয়াতের উপর হবে। (মুসলিম)
আরেকটি হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدَّ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَثِقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إلا أن تراجع.
‘নিশ্চয়ই যে লোক জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বাইরে চলে গেল সে ইসলামের রজ্জু তার গলদেশ থেকে খুলে ফেলল যতক্ষণ না সে পুনরায় ফিরে আসে। (আহমদ, তিরমিযী)
আরেকটি হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
بالجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِةُ.
‘তোমাদের জামাতবদ্ধ হয়ে থাকা কর্তব্য। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে নেকড়ে সহজেই খেয়ে ফেলে।’ (আবু দাউদ)
উপরের হাদীস তিনটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে ইসলামের রজ্জু গলদেশ থেকে খুলে ফেলা অথবা জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করার শামিল। তাছাড়া শয়তানী শক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষাও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব ইসলামের উপর টিকে থাকতে হলে সংঘবদ্ধ হওয়া ও সংঘবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।
উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, মুসলমানদের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকা একান্ত অপরিহার্য। সংঘবদ্ধতা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পালন ও দ্বীন কায়েম করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় মুসলমানদের উন্নতি, অগ্রগতি ও তাদের শত্রুদের মোকাবেলা। তাই ইসলাম ও মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের জন্যই সংঘবদ্ধতা অত্যাবশ্যক। এ হচ্ছে শরীয়তের দাবি ও নির্দেশনা। তাই প্রতিটি মুসলিমকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনে সচেতন ও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।
আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগঠনের গুরুত্ব
ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সংগঠনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সংগঠন ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো:
১. দাওয়াত সম্প্রসারণ: ইসলামী আন্দোলনের জন্য দাওয়াত ও প্রচার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর দ্বীনের দাওয়াত ব্যাপক ও কার্যকরভাবে দেয়ার জন্য সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দাওয়াত দান সহজ ও দ্রুত সম্ভব নয়। তাই বলা যায় দাওয়াত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সংগঠন অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা।
২. নেতৃত্ব সৃষ্টি: ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য যে ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন সে ধরনের নেতৃত্ব সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলা সহজ। সংগঠনের মাধ্যমে নেতৃত্ব তৈরি ও জনগণের সামনে নেতৃত্ব উপস্থাপিত হয়। বস্তুত নেতৃত্ব সংগ্রহ, বাছাই ও তৈরি করার ক্ষেত্রে সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৩. কর্মী সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ: সংগঠনের মাধ্যমে ময়দান থেকে আন্দোলনের কর্মী সংগৃহীত হয়। কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ও তাদেরকে আন্দোলনের উপযুক্ত কর্মীরূপে গড়ে তোলার কাজও সংগঠনের মাধ্যমে যত সহজে ও ব্যাপকভাবে করা সম্ভব হয় অন্য কোনভাবে এতটা করা সম্ভব হয় না। তাই কর্মী সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের জন্যও সংগঠনের প্রয়োজন।
৪. জনমত গঠন ও সঞ্চালন: আন্দোলনের জন্য জনমত অপরিহার্য। জনমত গঠন ও সঞ্চালন ছাড়া আন্দোলন অগ্রসর হতে পারে না, আর জনমত গঠন করা এবং জনমতকে সঞ্চালন ও কাজে লাগানো সংগঠনের মাধ্যমেই সহজ হয়। সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ছাড়া ব্যাপক জনমত সৃষ্টি যেমন দুরূহ তেমনই সংগঠন ছাড়া জনমতকে কাজেও লাগানো যায় না। তাই সংগঠন একান্ত প্রয়োজন।
৫. যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো: আন্দোলনের জন্য ইতিবাচক যত উপায়-উপকরণ আছে সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য সংগঠন প্রয়োজন, আন্দোলনের সম্ভাবনাকে বাস্তবে কাজে লাগাতে হলেও মজবুত-শক্তিশালী সংগঠন দরকার। হাজার সম্ভাবনা থাকলেও আন্দোলনের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হলে সেই সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। তাই শক্তিশালী সংগঠন একান্ত প্রয়োজন।
৬. অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন: আন্দোলন চালাবার জন্য ন্যূনতম অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োজন। সংগঠন ছাড়া অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো দুরূহ ব্যাপার। সংগঠন মজবুত হলে অর্থনৈতিক দূরাবস্থা অনেকটা কাটিয়ে ওঠা যায়। সংগঠন না থাকলে আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো সহজ হয় না। তাই অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের জন্যও সংগঠন প্রয়োজন।
৭. আন্দোলনকে ধরে রাখা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া: হঠাৎ কোন আন্দোলন জেগেও উঠতে পারে, সাড়াও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আন্দোলন ধরে রাখা সংগঠন ছাড়া সম্ভব নয়। সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন সংহত হয়। সাময়িক উত্তেজনা-উৎসাহ হ্রাস পেলেও আন্দোলনকে ধরে রাখা সম্ভব হয়। সংগঠন না থাকলে আন্দোলনকে দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায় না।
৮. আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দান: ইসলামী আন্দোলন একটি স্থায়ী আন্দোলন। দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্দোলন হয়। যদি আন্দোলন কোন ব্যক্তিনির্ভর হয় তাহলে ব্যক্তির অবর্তমানে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আন্দোলনের পেছনে শক্তিশালী সংগঠন থাকে তাহলে ব্যক্তি পরিবর্তন বা সময়ের ব্যবধানেও আন্দোলন শেষ হয় না; বরং সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দান করতে হলে সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন।
৯. রাজনৈতিক-সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি: ইসলামী আন্দোলনের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করতে হলে মজবুত সংগঠন প্রয়োজন। যে আন্দোলনের পেছনে কোন মজবুত সংগঠন নেই বা সংগঠন থাকলেও তা দুর্বল তার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুত্ব অত্যন্ত কম। মজবুত সংগঠন ছাড়া প্রভাব বিস্তার করা যায় না। আর সাময়িকভাবে তা করা গেলেও তা স্থায়ী হয় না। তাই প্রভাব সৃষ্টি ও প্রভাব বলয় সৃষ্টির জন্যও সংগঠন প্রয়োজন।
১০. বাধা-প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা: ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিতভাবেই অসংখ্য বাধা-প্রতিবন্ধকতা, জুলুম-নির্যাতনের মোকাবেলা করতে হবে। এ সমস্ত বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আন্দোলনকে অগ্রসর করার জন্য সংগঠন প্রয়োজন। সংগঠন মজবুত থাকলে বাধা-প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করা যায়। সাংগঠনিকভাবে মজবুত থাকলে জুলুম-নির্যাতন করে আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়া সহজ হয় না। প্রতিপক্ষের যাবতীয় আক্রমণও সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমে মোকাবেলা করা সহজ হয়। সংগঠন দুর্বল হলে এমনি ধরনের পরিস্থিতিতে আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও জুলুম-নির্যাতনের কার্যকর মোকাবেলার জন্য মজবুত সংগঠন প্রয়োজন।
১১. আশাবাদ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি: আন্দোলনকে অগ্রসর করার জন্য কর্মী বাহিনী ও জনগণের মধ্যে আশাবাদ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি প্রয়োজন। যে সমস্ত কারণে আশাবাদ সৃষ্টি হয় তার অন্যতম হচ্ছে মজবুত সংগঠন। সংগঠন শক্তিশালী হলে কর্মী বাহিনী আশান্বিত হয়। জনগণের আস্থা বেড়ে যায়। সামগ্রিকভাবে আশাবাদ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আর আশাবাদ বেশি হলে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিমাণও বেড়ে যায়। তাছাড়া পরিস্থিতির কারণে আন্দোলনে যদি কোন হতাশা দেখা দেয় তাহলে সংগঠনের মাধ্যমে তাও কাটিয়ে ওঠা যায়।
১২. ইসলামী ঐক্যের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা: ইসলামী আন্দোলন সফল করার জন্য ইসলামী ঐক্যের প্রয়োজন। আর ইসলামী ঐক্যের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য ইসলামী ঐক্যে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী মজবুত সংগঠনের প্রয়োজন। যারা সাংগঠনিকভাবে দুর্বল তাদের পক্ষ থেকে ঐক্যের আহ্বানে কেউ সাড়া দিতে চায় না। যদি শক্তিশালী কোন সংগঠন ঐক্যের আহ্বান জানায় বা আন্তরিকভাবে ঐক্যের প্রয়াস চালায় তাহলে ঐক্য প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজতর হতে পারে। অতএব ইসলামী ঐক্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হলেও একটি শক্তিশালী ঐক্যকামী সংগঠন প্রয়োজন।
মোটকথা ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগঠন একটি অপরিহার্য শর্ত। আন্দোলনে সংগঠনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংগঠন ছাড়া আন্দোলন গড়ে তোলা, আন্দোলনকে ধরে রাখা ও সফল করা দুরূহ ব্যাপার। সাংগঠনিক দুর্বলতা আন্দোলনের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই দ্বীনি আন্দোলনের জন্য একটি মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় হতে হবে।
কর্মসূচি ও নিয়মিত কার্যক্রম
একটি দ্বীনি সংগঠন গড়ে তুলতে হলে, একটি ইসলামী বিপ্লবকামী সংগঠন তথা ইকামতে দ্বীনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে হলে, সংগঠনকে অগ্রসর ও মজবুত করতে হলে স্থায়ীভাবে কতগুলো কর্মসূচি হাতে নিতে হয়। নিয়মিতভাবে কতিপয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। এসব কার্যক্রমের ভিত্তিতেই সংগঠন টিকে থাকে ও অগ্রসর হয়। সংগঠনের কর্মসূচি ও কার্যক্রমকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:
১. স্থায়ী বা সার্বজনীন কর্মসূচি,
২. পরিচালনামূলক কার্যক্রম,
৩. সাপ্তাহিক কর্মসূচি,
৪. গতিশীল ও মজবুতি অর্জনমূলক কার্যক্রম,
৫. মাঠ কর্মসূচি।
স্থায়ী ও সার্বজনীন কর্মসূচি
ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য, সার্বিক ক্ষেত্রে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মরত সংগঠনের জন্য প্রধানত চারটি স্থায়ী ও মৌলিক কর্মসূচি থাকা অপরিহার্য। এর কোন একটি বাদ দিয়ে ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী আন্দোলনের কাজ চলতে পারে না। সর্ব যুগের, সর্ব স্থানের আন্দোলনের ক্ষেত্রেই মৌলিক চারটি কর্মসূচি অত্যাবশ্যক। তাই এসব কর্মসূচি সার্বজনীন প্রকৃতির। এগুলো হচ্ছে-
১. দাওয়াত ও তাবলীগ: অর্থাৎ ইসলামী আদর্শের প্রচার, অন্যান্য আদর্শের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা, মানুষকে সচেতন করা, দ্বীন পালনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, খেলাফত তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি, ইসলামী আন্দোলনের সপক্ষে জনমত তৈরি, আন্দোলনের কর্মী সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম।
২. সংগঠিত করা: অর্থাৎ যারা খেলাফত তথা সার্বিক ক্ষেত্রে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে আগ্রহ ও উদ্বুদ্ধ হয় তাদেরকে সংঘবদ্ধ করা।
৩. প্রশিক্ষণ বা তালীম তরবিয়াত: অর্থাৎ আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত লোকদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দান, তাদের চরিত্র ও আমলের সংশোধন, তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার যথার্থ কর্মীরূপে তাদের গড়ে তোলা।
৪. জিহাদ: দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, খেলাফত অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন তথা ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ও আন্দোলন করা।
উপরোক্ত চারটি মৌলিক কর্মসূচি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন ও স্থায়ী কর্মসূচি। ইসলামী আন্দোলন করতে হলে এর প্রত্যেকটি কর্মসূচিই জরুরি। এর কোনটি বাদ দিলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন হবে না।
পরিচালনামূলক কার্যক্রম
একটি সংগঠনে নিয়মিতভাবে কতকগুলো প্রশাসনিক ও পরিচালনামূলক কাজ করতে হয়। এগুলো ছাড়া সংগঠন টিকে থাকে না। এসব কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-
ক. পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: প্রয়োজন, পরিস্থিতি ও উপায়-উপকরণের আলোকে পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গ্রহণ সংগঠন পরিচালনার জন্য অতীব জরুরি।
খ. কর্ম ও দায়িত্ব বণ্টন: কাজকে সুচারুরূপে সম্পাদন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জনের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ও কর্ম বণ্টন করা অত্যাবশ্যক। একাই কেউ সব কাজ করতে পারে না। দায়িত্ব ও কর্ম বণ্টনের ক্ষেত্রে কাজের প্রকৃতি ও চাহিদা, ব্যক্তির যোগ্যতা, সময়-সুযোগ, সক্রিয়তা ইত্যাদিকে সামনে রেখে দায়িত্ব ও কর্ম বণ্টন করতে হবে।
গ. নির্দেশনা ও যোগাযোগ: পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই গৃহীত সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি যথাসময়ে ও যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট সবার নিকট পৌছাতে হবে।
ঘ. তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ: পরিকল্পনা পৌছিয়ে বসে থাকলে চলবে না বরং কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না, কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে কি না ইত্যাদির খোঁজ-খবর রাখতে হবে। তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তত্ত্বাবধানের অভাব থাকলে কাজে শিথিলতা দেখা দেয়। নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই তত্ত্বাবধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ঙ. অর্থ সংস্থান: আন্দোলন ও সংগঠন চালাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই অর্থ সংগ্রহ করা ও যোগান দেয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
চ. সমন্বয় সাধন: সংগঠনের বিভিন্ন কাজ ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরি। সমন্বয়ের অভাবে অনেক সময় কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়। উপায়-উপকরণ যথাযথভাবে কাজে লাগে না। তাই কাজে সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন।
ছ. রিপোর্টিং ও পর্যালোচনা: পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে কাজের রিপোর্ট সংগ্রহ ও তৈরি করতে হয় এবং যথাযথ ফোরামে কাজের পর্যালোচনা করতে হয়।
একটি নিয়মিত সংগঠনে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়মিতভাবে সম্পাদন করতে হবে। বস্তুত পরিকল্পনা-সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গ্রহণ ছাড়া সংগঠনের কোন কাজ হবে না। আবার পরিকল্পনা করে বসে থাকলেই কাজ হবে না। এর জন্য পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্তে কর্ম বণ্টন করতে হবে, দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে এবং পরিকল্পনা-সিদ্ধান্তগুলো পৌঁছাতে হবে। পরিকল্পনা পৌঁছিয়ে দিলেই হবে না। কর্মসূচি, পরিকল্পনা-সিদ্ধান্ত ঠিকমত বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তার তত্ত্বাবধান করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে, যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ ও উৎসাহিত করতে হবে। কর্মসূচি/পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে। তার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর সময় শেষ হলে, কাজ শেষ হলে তার রিপোর্ট নিতে হবে এবং বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনার মাধ্যমে কাজের যে সমস্ত দুর্বলতা প্রকাশ পাবে ভবিষ্যতে তা দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এসব নিয়ম অনুসরণ করলে সহজে একটি সংগঠন গড়ে তোলা যাবে।
প্রাত্যহিক কার্যক্রম
ইকামতে দ্বীনের সংগঠনে কতকগুলো কাজ প্রাত্যহিক ও নিয়মিতভাবেই সম্পাদন করতে হবে। তা না হলে সংগঠন অগ্রসর হবে না। এগুলো হচ্ছে-
১. দাওয়াত ও প্রাথমিক সদস্য-কর্মী সংগ্রহ।’
২. সংগঠনের যে সমস্ত নিয়মিত রৈঠকাদী রয়েছে (যেমন: সাপ্তাহিক, মাসিক কর্মী সভাসমূহ, বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের বৈঠক ইত্যাদি) সেগুলো যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করা।
৩. সংগঠনের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে নিয়মিত বায়তুল মালের এয়ানত (আর্থিক সাহায্য) সংগ্রহ করা।
৪. বায়তুল মালের হিসাব রাখা।
৫. যে সমস্ত নিয়মিত কর্মসূচি রয়েছে তা ঠিকমত বাস্তবায়িত করা।
৬. সংগঠনের উর্ধ্বতন শাখা ও নিম্নতম শাখার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
৭. কর্মীদের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা ও তাদের তত্ত্বাবধান করা এবং অধঃস্তন শাখায় প্রয়োজনীয় সফর করা।
৮. কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি ও গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।
৯. কাজের রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট শাখায় পেশ ও উর্ধ্বতন শাখায় প্রেরণ করা।
গতিশীল ও মজবুতিমূলক কার্যক্রম
একটি সংগঠন দিন দিন অগ্রসর হতে হলে জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ এবং মজবুতী অর্জনের কাজও করতে হয়। যেমন উত্তরোত্তর কর্মী গঠন, কর্মীদের মানোন্নয়ন, বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও নেতৃত্ব সৃষ্টি, কাজের সিস্টেম গড়ে তোলা, মওসুমী কাজ না করে কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও স্থিতিশীলতা আনয়ন, সংগঠনকে মজবুত করা, কাজকে দিন দিন সম্প্রসারিত করা, সমাজের সর্বস্তরের লোকদেরকে সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, জনগণের নিকট সংগঠনের ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা। এসব কাজের মাধ্যমে একটি সংগঠন শক্তিশালী, মজবুত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে।
মাঠ কর্মসূচি
একটি ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন শুধু অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমেই ব্যাপৃত থাকবে না বরং অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে মাঠ কর্মসূচিও গ্রহণ করবে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: বিভিন্ন ইস্যুতে মিছিল-মিটিং, শোভাযাত্রা, জনসভা-বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশ, ধর্মঘট, হরতাল, ঘেরাও ইত্যাদি। মাঠ কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত তৈরি ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জিত হয়। সংগঠন ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। কর্মীদের মধ্যে গণমুখী, ময়দানমুখী ও সংগ্রামী যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তাই মাঠ কর্মসূচি সংগঠনের প্রসার ও মজবুতীর জন্য অপরিহার্য।
নেতৃত্ব
ইকামতের দ্বীনের সংগঠনের অন্যতম স্তর হচ্ছে নেতৃত্ব। নেতৃত্ব ছাড়া যেমন সংগঠন, আন্দোলন হয় না তেমনই নেতৃত্বের গুরুত্ব ইসলামী শরীয়তেও অত্যন্ত বেশি।
নেতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
ইসলামী শরীয়ত ও বাস্তব প্রয়োজন উভয় দিক বিচারেই নেতৃত্বের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। নেতৃত্ব যেমন শরীয়তের দাবি তেমনই বাস্তবে নেতৃত্ব ছাড়া সংস্থা, আন্দোলন, সমাজ, রাষ্ট্র কিছুই চলা সম্ভব নয়। নেতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:
১. নেতৃত্ব নির্বাচন বা নিয়োগ শরীয়তের নির্দেশ: ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের নেতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছে। নেতৃত্ববিহীন মুসলমানগণ জীবন যাপন করতে পারে না। এমনকি সফরের মত অস্থায়ী অবস্থায়ও নেতৃত্ব নিয়োগ করতে বলা হয়েছে:
إِذَا كَانَ ثَلَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِرُوا أَحَدَهُم.
‘সফরে এক সঙ্গে তিনজন লোক থাকলে তাদের মধ্য থেকে যেন একজনকে আমীর করে নেয়।’ (আবু দাউদ)
এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী বিশেষজ্ঞ ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দল যতই ক্ষুদ্র হোক, তারা একান্ত অস্থায়ী অবস্থায় থাকুক যে কোন অবস্থাতেই তাদের মধ্য থেকে একজন আমীর নিযুক্ত করে নেয়া ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন। এটা এজন্য যে অন্যান্য সব দলের পক্ষে যেন তা সতর্কবাণীরূপে গণ্য হয় যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মাত্র তিন ব্যক্তি জমায়েত হলেও যে ক্ষেত্রে আমীর বা নেতা নির্বাচন ওয়াজিব সে ক্ষেত্রে অন্যান্য জামাতের উপর এ হুকুম কার্যকর করা আরো অধিক প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ পাক সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর আমীর ছাড়া অন্যান্যদের সাথে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে জিহাদ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, হজ্জ পালন, জুমা ও দুই ঈদের নামায কায়েম করা, আর্ত-নির্যাতিতের সাহায্য, হদ কার্যকর করা ইত্যাদি ফরয-ওয়াজিবসমূহ শক্তি ও নেতার নেতৃত্ব ছাড়া বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। (ইমাম ইবনে তাইমিয়া: আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়া ২৮ তম পরিচ্ছেদ)
অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
لا يَحِلُّ الثَّلَاثَةِ يَكُونُ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ إِلَّا امَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُم.
‘তিনজন লোক কোন বিজন এলাকায় থাকলেও তাদের মধ্য থেকে কাউকেও আমীর নিয়োগ না করে বাস করা জায়েয নয়।’ (মুসনাদে আহমদ)
বিভিন্ন দলিল পর্যালোচনা করে ইমাম শাওকানী লিখেছেন:
انَّهُ يَجِبُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصبُ الْآئِمَةِ وَالْوَلَاةِ وَالْحُكَامِ.
‘নেতা নির্বাচন, দায়িত্বশীল ও বিচারক নিয়োগ করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব।’ (নাইলুল আওতার: খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৫৭)
নেতৃত্বের এ গুরুত্বের কারণেই প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য আকায়েদের কিতাব শরহে আকায়েদে নফসীতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম নিয়োগ বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা যে ওয়াজিব এ কথার উপর ইজমা হয়েছে:
ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب.
‘অতঃপর এ কথার উপর ইজমা হয়েছে যে, ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব।’
এর কারণ ব্যাখ্যা করে ইমাম তাফতাযানী (রহ.) লিখেছেন: ‘সঠিক মাযহাব এই যে, এটা (অর্থাৎ নেতৃত্ব) বান্দার উপর নকলী দলিলের দ্বারা ওয়াজিব। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:
من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية.
‘যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে সেই যুগের ইমামকে সে জানে না তাহলে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুই বরণ করল এবং এজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহাবাগণ ‘ইমাম’ নির্বাচন করার ব্যাপারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকি নবীজীর দাফনের উপরও এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এমনিভাবে প্রত্যেক ইমামের মৃত্যুর পর এবং এ কারণে এটা ওয়াজিব যে, বহু ওয়াজিবাতে শরীয়া এর উপর নির্ভরশীল।’ (শরহে আকায়েদে নফসী ইমাম তাফতাযানী, খণ্ড ২)
অতএব ইমাম বা নেতৃত্ব নিয়োগ যে ইসলামী শরীয়তের একটি অপরিহার্য বিষয় তাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।
২. নেতৃত্ব ঢাল স্বরূপ: বাস্তব ক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুরুত্ব এ কারণে যে নেতৃত্ব সমাজের বা সংগঠনের জন্য ঢালস্বরূপ কাজ করে। যেমন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
روستا وإِنَّمَا الإِمَامُ جَنَّةٌ يُقَاتِلُ مِن وَرَانِ وَيَتَّقى به
‘প্রকৃতপক্ষে ইমাম হলো ঢালস্বরূপ।। তার পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর দ্বারা (বিপদ-আপদ) থেকে নিরাপত্তা অর্জন করা যায়।’ (বুখারী-মুসলিম)
কাজেই নেতৃত্ব ছাড়া মুসলমানদের কার্যকর অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে যেমন ঢাল ছাড়া একজন সৈনিকের আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত সুকঠিন। এ হাদীস থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, নিরাপত্তার জন্যও নেতৃত্ব অপরিহার্য।
৩. ইসলামের সামষ্টিক ইবাদতের জন্য নেতৃত্ব অপরিহার্য: ইসলামে নেতৃত্বের গুরুত্ব এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইসলাম যেসব ইবাদত ফরয করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ নেতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধভাবে করাকে আবশ্যক করে দিয়েছে। যেমন জামাতের সাথে নামায আদায়, জুমা, দুই ঈদ, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি। কাজেই যেখানে খালেছ ইবাদতও নেতৃত্বের অধীনে করা জরুরি সেখানে অন্যান্য বিষয়ে নেতৃত্বের গুরুত্বও তো আরো বেশি হওয়ারই কথা।
৪. নেতৃত্ববিহীন সংগঠন অবাস্তব: নেতৃত্ব ছাড়া কোন সংগঠন, সংস্থা, কায়েম, পরিচালনা ও মজবুতি অর্জন করা সম্ভব নয়। নেতৃত্ব ছাড়া কোন সংগঠনের চিন্তা করা অবাস্তব। তাই হযরত ওমর (রাযি.) লিখেছেন:
لا اسلام إِلَّا بِجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةُ إِلَّا بِإِمَارَةِ.
‘জামাতবদ্ধতা ছাড়া ইসলাম হয় না। নেতৃত্ববিহীনও সংগঠন হয় না।’
কাজেই দ্বীনি উদ্দেশ্যে কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, পরিচালনা করতে চাইলে নেতৃত্ব অপরিহার্য।
৫. নেতৃত্ব ছাড়া আন্দোলনের সফলতা অসম্ভব: ইসলামী আন্দোলন সফল করতে হলে সঠিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। কোন নেতৃত্ব না থাকলে বা দুর্বল নেতৃত্ব হলে আন্দোলনের সফলতা সুদূর পরাহত। তাই আন্দোলনের জন্য নেতৃত্ব অত্যাবশ্যক।
৬. জনগণ নেতৃত্বের দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়: একটি আন্দোলন বা সংস্থার কার্যকারিতা বা জনপ্রিয়তা অনেকটা নির্ভর করে নেতৃত্বের মান ও জনপ্রিয়তার উপর। জনগণ নেতৃত্বের দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়। নেতৃত্ব আস্থাভাজন হলে, জনগণ আন্দোলনের প্রতি বেশি আস্থাশীল হতে পারে। নেতৃত্ব দুর্বল, অযোগ্য অথবা অগ্রহণযোগ্য হলে আন্দোলনের প্রতি, সংগঠনের প্রতি আস্থা ও আকর্ষণ কমে যাবে। কাজেই সংগঠনের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টি করতে হলেও যোগ্য নেতৃত্ব প্রয়োজন।
৭. সংগঠন- আন্দোলনের সংহতির জন্য: নেতৃত্ব ছাড়া আন্দোলন-সংগঠন কোন অবস্থায়ই সংহত হতে পারে। সংহতি রক্ষাও সম্ভব হয় না। সংগঠনের সংহতি প্রধানত নির্ভর করে নেতৃত্বের উপর।
ইসলামী নেতৃত্বের প্রকৃতি
১. নেতৃত্ব একটি আমানত ও দায়িত্বপূর্ণ বিষয়: ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
.. فالإمام الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِهِهِ.
‘সুতরাং জনগণের ইমামও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। (কিয়ামতের দিন) তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে...।’ (বুখারী, মুসলিম)
অন্য একটি হাদীসে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্বের বিষয়টি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক লোকের ওয়ালী (অভিভাবক-নেতা) কিয়ামতের দিন তার গলায় শিকল পরা অবস্থায় সে উত্থিত হবে। তার হাত নিজের ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। তাকে এ অবস্থা থেকে একমাত্র তার নেক আমলই (ইনসাফ ও ন্যায়নীতি) মুক্ত করতে পারবে অথবা তার কৃত গোনাহ তাকে ধ্বংস করবে। (আহমদ)
অতএব নেতৃত্বের দায়িত্বটি অতীব নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক ও হুঁশিয়ার হতে হবে।
২. পদের লোভ নিষিদ্ধ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পদলোভ নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়। কেউ পদ চেয়ে নিলে তার দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে ছেড়ে দেয়া হয় আর না চাইতে দায়িত্ব আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয়। একদা একজন প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةِ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ و اعطيتها عَنْ غَيْر مَتَكَةٍ أُعِنَتْ عَلَيْهَا.
‘নেতৃত্ব বা পদে চেয়ে নিও না। কেননা যদি তোমাকে তা চাওয়ার কারণে দেয়া হয়, তবে তা তোমার উপর সোপর্দ করা হবে, আর যদি তা চাওয়া ব্যতিরেকে দেয়া হয়, তাহলে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে।’ (বুখারী, মুসলিম)
আরেকটি হাদীসে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন ব্যক্তির পদ প্রার্থনার প্রেক্ষিতে বলেন:
إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا العمل احدا سأله ولا احدا حرص عليه.
‘আল্লাহর কসম! আমরা এই কাজে (শাসক পদে) এমন কাউকে নিয়োগ করি না যে তার প্রার্থী হয় এবং ঐ ব্যক্তিকেও না যে তার জন্য লালায়িত হয়।’ (বুখারী, মুসলিম)
৩. নেতা-কর্মীর সম্পর্ক ভালোবাসার: জনগণ ও কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ধরনের নেতৃত্ব উত্তম এবং কোন ধরনের নেতৃত্ব নিকৃষ্ট তার পরিচয় হাদীসে অস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে:
رور الذين يحبونهم ويُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ خبار المتكم الذين تحبونهم و وَشِرَار انتكم الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ويصلون عليكم وشرارا تلعنونهم ويلعنونكم.
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমাদের নেতাদের বা শাসকদের মধ্যে সেই উত্তম যাকে তোমরা ভালোবাস আর যারা তোমাদিগকে ভালোবাসে। আর তোমরা তাদের জন্য দুআ করো তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের সেই শাসক বা নেতারাই মন্দ যদি তাকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। আর তোমরা তাদের প্রতি অভিশাপ করো এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ করে।’ (মুসলিম)
৪. ন্যায়পরায়ণতা সর্বোত্তম নেতৃত্বের মাপকাঠি: কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসক বা নেতৃত্ব আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম বিবেচিত হবে। অন্য দিকে জালেম শাসক হবে সবচেয়ে ঘৃণিত ও মন্দ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন:
ان احب النَّاسَ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلُ وان ابغض الناس إلى الله يوم الْقِيَامَةِ أَشَدُّهُمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجلِسًا امام جائر
‘কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ ইমাম হবেন আল্লাহর কাছে সমস্ত লোকের চেয়ে প্রিয়তম তাঁর নিকটতম মর্যাদার অধিকারী। আর কিয়ামতের দিন অত্যাচারী জালেম শাসকই হবে আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষের চেয়ে সর্বাধিক ঘৃণিত ও কঠোরতম আয়াবের অধিকারী।’
অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তারা আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী হবে। (তিরমিযী)
আর একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
إن شر الرعاء الحطمة.
‘সর্বাধিক মন্দ শাসক বা নেতা হচ্ছে যারা নির্যাতনকারী।’ (মুসলিম)
নেতৃত্বের কাজ
একটি ইকামতে দ্বীনের সংগঠনের নেতৃত্বকে বহুবিধ কার্য সম্পাদন করতে হয়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ:
১. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হচ্ছে সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রয়োজন মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
২. পরামর্শ করে কাজ করা: নেতৃত্বকে অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিমত বা স্বেচ্ছাচারিতার সাথে কাজ করলে, সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলনের, সংগঠনের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।
৩. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিধান: নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হচ্ছে সংগঠনে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রাখা, অনিয়মসমূহের পথ বন্ধ করা, অনিয়ম সৃষ্টি হলে তা দূর করা, সংগঠনের গঠনতন্ত্রের অনুসৃতির নিশ্চয়তা বিধান।
৪. তত্ত্বাবধান: নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান করা। কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কাজ যাতে অগ্রসর হয়, কর্মসূচি যাতে যথাযথ বাস্তবায়িত হয় তার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।
৫. কর্ম গঠন ও উত্তম-যোগ্য সহকর্মী সংগ্রহ: নেতৃত্বের আরেকটি কাজ হচ্ছে কর্মীদেরকে গঠন করা, তাদেরকে আন্দোলনের যোগ্য কর্মীরূপে গড়ে তোলা। সাথে সাথে উত্তম ও যোগ্য সহকর্মী বাছাইও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরবর্তী দায়িত্বশীল গড়ে তোলাও নেতৃত্বেরই দায়িত্ব।
৬. জনশক্তি ও উপায়-উপকরণের যথাযথ ব্যবহার: নেতৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সংগঠনে জনশক্তি ও উপায়-উপকরণ যা আছে তার সঠিক ব্যবহার। জনশক্তি ও উপায়-উপকরণ যাতে অপচয় না হয়, অব্যবহৃত না তাকে তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৭. অর্থ সংস্থান: সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের দায়িত্ব নেতৃত্বের। নেতৃত্বকেই আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হয়, তার ব্যবস্থা করতে হয়।
৮. কাজের সিস্টেম গড়ে তোলা: নেতৃত্বের আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে সংগঠন ও তার কাজকে একটি সিস্টেমের উপর দাঁড় করানো। সিস্টেমবিহীন কাজ যতই বেশি হোক তার বরকত কম, স্থায়িত্ব কম। সিস্টেম না থাকলে কাজ ধরে রাখা দুষ্কর। তাই সিস্টেম গড়ে তোলার ব্যাপারে নেতৃত্বকে পদক্ষেপ নিতে হবে।
৯. অনুকূল জনমত তৈরি ও জনগণকে সঞ্চালিত করা: আন্দোলন সফলতার জন্য জনমত অপরিহার্য। তাই নেতৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আন্দোলনের পক্ষে, সংগঠনের অনুকূলে জনমত তৈরি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে সংগঠিত ও সঞ্চালিত করা। জনমত তৈরির ক্ষেত্রে নেতৃত্বকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এটি নেতৃত্বেরই দায়িত্ব। নেতৃত্বের সফলতা ব্যর্থতাও অনেকটা নির্ভর করে অনুকূল জনমত তৈরি ও সংগঠিত করার সামর্থ্যের উপর। তাই এ বিষয়টি নেতৃত্বের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
১০. সংগঠনের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা: সংগঠনের অগ্রগতির জন্য ইতিবাচক ভাবমূর্তি অত্যন্ত প্রয়োজন। নেতৃত্বের উপর অনেকটা ভাবমূর্তি নির্ভর করে। নেতৃত্বের দায়িত্ব সংগঠনের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। তাই সংগঠনের ভাবমূর্তি যাতে বৃদ্ধি পায়, ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুন্ন না হয়, তার জন্য নেতৃত্বকে সচেষ্ট ও সতর্ক থাকতে হবে।
১১. উত্তরোত্তর সংগঠনকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া: যে লক্ষ্যে সংগঠন কায়েম হয়েছে সে লক্ষ্যের দিকে এগোনোই সংগঠনের কাজ। যদি লক্ষ্যের দিকে দিন দিন এগোনো সম্ভব না হয়, তাহলে সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংগঠনের সমস্ত কাজের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দ্বীন কায়েমের মহান লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। তাই নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে সংগঠন যাতে উত্তরোত্তর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়, তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সংগঠন যাতে লক্ষ্য বিচ্যুত না হয় সে দিকে সতর্ক থাকা। সংগঠন পরিচালনার সফলতা হচ্ছে সংগঠন লক্ষ্যপাণে এগিয়ে যাবে, দিন দিন লক্ষ্য অভিমুখে সংগঠন অগ্রসর হতে থাকবে।
নেতৃত্বের গুণাবলী
ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের যিনি বা যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদের কতিপয় মৌলিক গুণ ও যোগ্যতা থাকতে হবে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:
১. ইলম ও হেকমত: ইসলামী আন্দোলনের ও সংগঠনের নেতৃত্বের জন্য কুরআন-সুন্নাহর পরিচ্ছন্ন ও পর্যাপ্ত জ্ঞান অপরিহার্য। দ্বীন-দুনিয়া বোঝার ক্ষমতা তার থাকতে হবে। যে ব্যক্তি মূর্খ ও নির্বোধ সে ব্যক্তি নেতৃত্বের উপযুক্ত নয়। এমন ব্যক্তির হাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই দেয়া যেতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহ থেকে নেতৃত্বের জন্য ইলম ও হেকমতের অপরিহার্যতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।
পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের শাসক হিসেবে হযরত তালুতকে নিয়োগ দান করলে বনী ইসরাঈলীরা এতে আপত্তি উত্থাপন করে। তালুতের নিয়োগের যৌক্তিকতা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন যে, তাকে জ্ঞানের ও শক্তির প্রাচুর্য দান করা হয়েছিল:
ان الله اصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَشَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.
‘আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে (শাসক হিসেবে) পছন্দ করেছেন, বাছাই করেছেন এবং তাকে ইলম ও শারীরিক দিক থেকে প্রাচুর্য দান করেছেন।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ২৪৭)
হযরত দাউদ (আ.) কে আল্লাহ রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়েছিলেন। তৎসঙ্গে দিয়েছিলেন হেকমত ও ইলম:
واله الله الملك وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاء
‘আল্লাহ তাকে (দাউদকে) রাষ্ট্রক্ষমতা দান করলেন, দান করলেন হেকমত ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ২৫১)
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর খাদ্য ভাণ্ডারের দায়িত্ব চাওয়া প্রসঙ্গে বলেন:
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ - إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
ইউসুফ (আ.) বললেন: আমাকে যমীনের ভাণ্ডারসমূহের দায়িত্ব প্রদান করুন। (কেননা) আমি হেফাযতকারী এবং জ্ঞানও রাখি।’ (সূরা ইউসুফ: আয়াত ৫৫)
যারা জ্ঞানী-ইলমের অধিকারী তাদের মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন:
يرفع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ - وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتِ.
‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন।’ (সূরা মুযাদিলা: আয়াত ১১)
যারা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেতৃত্ব তো তারাই দেবে। অন্য আয়াতে জানানো হয়েছে যে, ইলমের অধিকারী ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি মর্যাদায় সমান নয়।
والذين لا يعلمون. قل هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَا
‘বল, যাদের জ্ঞান আছে আর যাদের জ্ঞান নেই তারা কি সমান হতে পারে?’ (সূরা যুমার: আয়াত ৯)
হাদীসে আছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
إِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الأَنبياء
‘আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী।’ (তিরমিযী)
অন্য হাদীসে লোকদের ইমাম বা নেতা কে হবে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:
يَوْمِ الْقَوْمَ أَقْرَأَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ.
‘লোকদের ইমাম (নেতা) হবে সে ব্যক্তি যে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে সমান হলে সে-ই নেতা হবে যে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ।
অন্য দিকে অজ্ঞ, জাহেল, নির্বোধ ব্যক্তির নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সোপর্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
ولا توبوا السُّفَهَا، أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيمَا.
‘যে ধন-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-জীবিকার অবলম্বন করেছেন তা নির্বোধ ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিও না।’ (সূরা নিসা: আয়াত ৫)
এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যেখানে নির্বোধদের হাতে ধন-সম্পদের মতো বিষয় তুলে দিতে নিষেধ করা হচ্ছে সেখানে নেতৃত্বের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিভাবে নির্বোধ, অজ্ঞ-মূর্খদের হাতে দেয়া যেতে পারে? মোটকথা ইসলামী নেতৃত্বের জন্য কুরআন-সুন্নাহর পর্যাপ্ত জ্ঞান, তা প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞান, যুগ ও দুনিয়ার চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুধাবন এবং সমস্যার সমাধান দানের যোগ্যতা, সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্যতাসহ দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনীয় জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। শুধু কিতাবী বা পুঁথিগত জ্ঞান নয়, তা প্রয়োগের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। অর্থাৎ ইলমের সাথে ইকামত ও (প্রজ্ঞা) থাকা নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য।
২. আদালত ও তাকওয়া: ইসলামী নেতৃত্বের জন্য ইলমের সাথে সাথে আমলকারী হওয়াও প্রয়োজন। নেতৃত্ব যিনি দেবেন তাকে অবশ্যই আদালত ও তাকওয়ার গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। যিনি ফাসেক-জালেম-মুফসিদ তিনি ইসলামী সমাজের নেতৃত্বের অনুপযুক্ত। এমন ব্যক্তিদের অনুসরণ করা যেতে পারে না। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা দ্ব্যর্থহীন।
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرَطًا.
‘এমন লোকদের আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি। যে তার নফসের কামনা-বাসনার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।’ (সূরা কাহাফ: আয়াত ২৮)
অন্যত্র বলা হয়েছে:
ولا تطيعوا أمر المسرفين - الذين يفسدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يصلحون.
‘সেসব সীমালঙ্ঘনকারীদের আনুগত্য করো না, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সংস্কার-সংশোধন করে না।’ (সূরা শুআরা: আয়াত ১৫১-১৫২)
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, মুত্তাকী লোকেরাই হচ্ছে সর্বাধিক সম্মানিত:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله اتقدم.
‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।’ (সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩)
অতএব মুত্তাকী ব্যক্তিই মুসলমানদের নেতৃত্বের উপযুক্ত। অন্য একটি আয়াতে মুমিনদের এভাবে দুআ করতে শিখানো হয়েছে:
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للمتقين إماما .
‘এবং আমাদিগকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানাও। অর্থাৎ তাকওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রসর কর, নেতৃত্ব দান কর। মোটকথা নেতৃত্বের জন্য ইসলামের বিধি-বিধানের যথাযথ অনুসৃতি (তথা আদালত) এবং (খোদাভীতি) পরহেযগারী (তথা তাকওয়া) থাকা আবশ্যক। আদেল ও মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। প্রধান নেতৃত্ব ‘ইহসানের’ মানে উত্তীর্ণ হতে হবে। চারিত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে তিনি হবেন পবিত্র, পরিশুদ্ধ, অনুসরণীয়। প্রয়োজনীয় সৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটবে নেতৃত্বের মধ্যে।’
৩. সংগ্রামী ও মুজাহিদ তথা সক্রিয়তা: ইসলামী আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদেরকে অবশ্যই আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে হবে। তাদেরকে সংগ্রামী ও মুজাহিদ চরিত্রের হতে হবে। ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। যারা নিজেরা জিহাদী চরিত্রের নন, যারা জিহাদ ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে পিছপা, যারা সংগ্রামবিমুখ, নিষ্ক্রিয়, স্থবির, ত্যাগ ও কুরবানী করতে কুণ্ঠিত, যারা আল্লাহর পথে সংগ্রামে পিছিয়ে আছেন তাদের পক্ষে দ্বীনি আন্দোলনের যথার্থ নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। কেননা যারা আল্লাহর পথে যে কোন ত্যাগ-কুরবানী করেন, জিহাদ করেন তাদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা।
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - أُولَئِكَ يَرْجُونَ رحمت الله.
‘যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছে, তাঁর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত লাভের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ২১৮)
ان الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتَلُونَ.
‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের নিকট থেকে তাদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মারে ও মরে।’ (সূরা তাওবা: আয়াত ১১১)
যেহেতু জিহাদ ও আন্দোলন ঈমানের অনিবার্য দাবি তাই জিহাদের কাজে, আন্দোলনের কাজে যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদেরকে এ ক্ষেত্রে অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে হবে। যে সংগঠনের উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্যে সংগ্রাম করা সে আন্দোলনের নেতৃত্ব সংগ্রামবিমুখ, নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।
৪. সংগঠনের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও আমানতদার: নেতৃত্ব একটি বিরাট আমানত। এ আমানত এমন ব্যক্তিদের হাতেই দিতে হবে যারা এর জন্য উপযুক্ত। যারা দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত নন- তা মানসিক, চারিত্রিক, দৈহিক যে কোন কারণেই হোক না কেন, তাদের নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যারা নেতৃত্বের আমানত বহন করার মতো উপযুক্ত তাদেরকে এ দায়িত্ব দিতে হবে।
আল্লাহ পাকের নির্দেশ:
ان الله يا مومهم أن تُؤَدُّوا الْآمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا .
‘আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানতসমূহ যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট সোপর্দ কর।’ (সূরা নিসা: আয়াত ৫৮)
হযরত ইউসুফ (আ.) দায়িত্ব চাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর নিজের যে দু’টো যোগ্যতার কথা বলেছিলেন তার প্রথমটি ছিলো:
اني حفيظ
‘আমি হেফাযতকারী।’ (সূরা ইউসুফ: আয়াত ৫৫)
কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, দায়িত্ব পালনের মতো যোগ্যতা-নেতৃত্ব যারা দেবেন তাদের মধ্যে আমানতদারী থাকতে হবে। মোটকথা আমানতদার, দায়িত্ব পালন করার যোগ্য লোকদেরই নেতৃত্ব নিতে হবে। অযোগ্য লোকদেরকে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না।
৫. দৈহিক যোগ্যতা: ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার মতো দৈহিক যোগ্যতা, কর্মক্ষমতাও নেতৃত্বের থাকতে হবে। যিনি শারীরিক কারণে দায়িত্ব, পালন করতে অপারগ তাঁর পক্ষে নেতৃত্ব দান সম্ভব নয়। পূর্বেই আমরা তালুত প্রসঙ্গে দেখেছি যে, আল্লাহ তালুতকে দুই ধরনের যোগ্যতা দিয়েছিলেন- জ্ঞান ও দৈহিক শক্তিতে প্রাচুর্য। (সূরা বাকারা: আয়াত ২৪৭)
কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইলমের সাথে সাথে দায়িত্ব পালন করার মতো দৈহিক যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।
৬. হৃদয়বৃত্তিক যোগ্যতা: ইসলামী নেতৃত্ব শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক দিক থেকে যোগ্য হলেই চলবে না; বরং প্রয়োজনীয় হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হতে হবে। তার স্বভাব-প্রকৃতি হবে সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তার হৃদয় হবে ভালবাসায় পূর্ণ। সহানুভূতি-সহমর্মিতা হবে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার হবে মার্জিত। মনের কাঠিন্য থেকে তিনি থাকবেন মুক্ত। উগ্র স্বভাব, পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী লোকদেরকে কাছে টানার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেয়। অন্যান্য শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে তিনি যদি গ্রহণযোগ্য না হন, আকর্ষণ করার মতো চরিত্র, মানবিক গুণ যদি না থাকে, মনের প্রশস্ততার যদি থাকে অভাব তবে লোকদের ধরে রাখা তার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া সহকর্মীদের প্রতি সহনশীল না হলে, তাদের ভুল-ত্রুটি হৃদয়ের ঔদার্য দ্বারা ক্ষমাশীলতার সাথে গ্রহণ না করলে, সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ না করলে একদিকে আন্দোলন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্য দিকে নেতৃত্বও তেমনই অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। তদুপরি গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন ও আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভরসা ইসলামী নেতৃত্বের জন্য অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন। স্বৈরাচারী, আত্মকেন্দ্রিক, পাষাণ হৃদয়, রূঢ় চরিত্রবিশিষ্ট নেতৃত্ব ইসলামে অচল। নেতৃত্বের এ বৈশিষ্ট্যগুলোই নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে:
فَبِمَا رَحۡمَۃٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَ لَوۡ كُنۡتَ فَظًّا غَلِیۡظَ الۡقَلۡبِ لَانۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِكَ ۪ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَ اسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَ شَاوِرۡهُمۡ فِی الۡاَمۡرِ ۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَی اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُتَوَكِّلِیۡنَ
‘(হে নবী!) এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের জন্যে খুবই নম্র স্বভাবের হয়েছ। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতে তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই এদের অপরাধ মাফ করে দাও, তাদের মাগফিরাতের জন্যে দুআ করো। কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর। যখন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর।’ (সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১৫৯)
উপরের আয়াতে নেতৃত্বের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে লোকদের, কর্মীদের ধরে রাখা, সংহত ও ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত এবং যা করণীয় তা হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
নেতৃত্বের সাধারণ গুণাবলী ও যোগ্যতা
যে কোন আন্দোলন ও সংগঠনে দেয়ার জন্যে বিশেষ কতকগুলো গুণ বৈশিষ্ট্য য যোগ্যতার দরকার হয়। ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য না থাকলে সফল নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হয় না। যে কোন নেতৃত্বের জন্যে এগুলো প্রয়োজন হয়। এ জাতীয় অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নোক্তগুলো সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।
১. উদ্যোগী চরিত্র: নেতৃত্ব দিতে হলে উদ্যোগী হতে হবে। যার উদ্যোগী চরিত্র নেই, যিনি নিষ্ক্রিয় তার পক্ষে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। যিনি উদ্যোগ নেবেন তার নেতৃত্বই গ্রহণযোগ্য হয়। তাই আন্দোলন-সংগঠনের নেতৃত্বকে অবশ্যই উদ্যোগী চরিত্রের হতে হবে। উদ্যোগ হচ্ছে নেতৃত্বের চাবিকাঠি।
২. প্রয়োজনীয় ঝুঁকি বহন ও সাহসিকতা: নেতৃত্ব একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। যিনি ঝুঁকি নিতে ভয় পান, যার ঝুঁকি নেয়ার মত সাহস নেই তার পক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হয় না। তাই ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা ও সাহসিকতা নেতৃত্বের জন্যে অতীব প্রয়োজন।
৩. ভাল বক্তা: নেতৃত্ব দেবার জন্য, জনগণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, বক্তৃতা দেয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত বড় গুণ। তাই যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকে অন্যান্য গুণাবলীর পাশাপাশি ভাল বক্তা হওয়ার গুণ অর্জন করতে হবে।
৪. সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা: নেতৃত্বের জন্য অবশ্যই সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক গুণ ও যোগ্যতা থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, মানুষ পরিচালনার যোগ্যতা, শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা, সবাইকে নিয়ে চলা, পরিস্থিতি মোকাবেলা করার যোগ্যতা ইত্যাদি হচ্ছে নেতৃত্বের জন্য আবশ্যিক সাংগঠনিক প্রশাসনিক গুণ। এগুলো ছাড়া সফল নেতৃত্ব দেয়া কঠিন।
বস্তুত ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলনের নেতৃত্বকে দ্বীনি ও মানবিক উভয় ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, উভয় ধরনের গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।
নেতৃত্ব নির্বাচন
একটি দ্বীনি সংগঠনে নেতৃত্ব নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিপূর্বে নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে একটি সংগঠনে হয়ত সব সময় এ ধরনের লোক নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে কাজ বন্ধ করা যাবে না, আর কাজ করতে হলে নেতৃত্ব প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায় সংগঠনের মধ্যে থেকেই উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধানত যে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, তন্মধ্যে রয়েছে- ব্যক্তির ইলম, তাকওয়া-পরহেযগারী, আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা, সাংগঠনিক গুণাবলী ও আন্দোলনের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি। এসব গুণাবলীর দিক থেকে তুলনামূলকভাবে যারা অগ্রসর তাদেরকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। মনে রাখা দরকার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, অর্থনৈতিক শক্তি ইসলামী নেতৃত্বের আসল বিষয় নয়। আসল বিষয় হচ্ছে দ্বীনি ও সাংগঠনিক যোগ্যতা। কাজ চলার জন্যই নেতৃত্ব। তাই কাজ যাদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে, যাদের নেতৃত্বে কাজ অগ্রসর হবে তাদেরকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।
আর যারা নেতৃত্বের জন্য প্রয়াসী হয়, যারা নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য তদবির চালায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রুপিং করে তারা দ্বীনি নেতৃত্বের অনুপযুক্ত। তাদের অন্যান্য যোগ্যতা যতই থাক না কেন?
মোটকথা আন্দোলন ও সংগঠনের প্রয়োজনকে সামনে রেখে সম্ভাব্য যোগ্য ও সক্রিয় লোকদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা উচিত।
প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে এমন অনেক লোককেই দায়িত্ব প্রদান করতে হয় যারা হয়ত নেতৃত্বের সব শর্ত পূরণ করতে অপারগ। তবুও আন্দোলন-সংগঠনের কল্যাণ বিবেচনা করেই এ ধরনের লোকদের উপর দায়িত্ব প্রদান করতে হয়। কিন্তু এটা হচ্ছে সাময়িক ব্যাপার। আন্দোলন ও সংগঠন অগ্রসর হলে যোগ্য নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবেই আশা করা যায়।
নেতৃত্ব নির্বাচন প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় হচ্ছে নেতৃত্ব নির্বাচন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক মোটেই বিবেচনায় আনা উচিত নয়। পরিপূর্ণ আমানতদারীর সাথে সংগঠন ও আন্দোলনের কল্যাণ বিবেচনা করেই নেতৃত্ব নির্বাচন করা উচিত। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহর রহমতে সঠিক নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে।
আনুগত্য ও শৃঙ্খলা
আনুগত্য ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন-সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্তদের আনুগত্য করা অপরিহার্য। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পরই উলিল আমরের আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে।
اطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
‘আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর তাদের আনুগত্য কর।’ (সূরা নিসা: আয়াত ৫৯)
উপরোক্ত আয়াত স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, উলিল আমর বা আদেশ দেয়ার কার্যাদির সম্পাদন ও পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের আনুগত্য করতে হবে। এ আনুগত্য ওয়াজিব। নেতৃত্বের আনুগত্যের মাধ্যমে বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা হয়। হাদীসে আছে:
ومن يطع منْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ : الأميرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.
‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহকেই অমান্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো, যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।’ (বুখারী-মুসলিম)
পছন্দ-অপছন্দ সর্বাবস্থায়ই আনুগত্য অবশ্য করণীয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
عَلَى المرء المسلم السمع والطاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَن المُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ.
‘মুসলিম ব্যক্তির (নেতার) আদেশ শোনা ও মানা কর্তব্য, চাই (সে আদেশ) তার পছন্দনীয় হোক কিংবা অপছন্দনীয় হোক অবশ্য নাফরমানীমূলক আদেশ ছাড়া।’ (বুখারী ও মুসলিম)
অকারণে আনুগত্যের বন্ধন খুলে ফেলা আখেরাতের ক্ষতির কারণ:
قَالَ مَنْ خَلَغَ بَدَا مَنْ طَاعَةَ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُبَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وليسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةَ مَانَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّة
(নবী কারীম [সা.]) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বায়আত ছাড়া মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।’ (মুসলিম)
সামাজিকভাবে নিম্নস্তরের কেউ দায়িত্বশীল হলে বা নেতৃত্বে সমাসীন হলেও আনুগত্যের শিথিলতা দেখানো যাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
اشتعوا واطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبيبي كَانَ رَاسَهُ زَينَة.
‘যদি এমন কোন হাবশী দাসকেও তোমাদের নেতা বানিয়ে দেয়া হয় যার মস্তক কিসমিসের ন্যায় ক্ষুদ্র, তথাপি তোমরা তার প্রতি অনুগত থাকবে।’ (বুখারী)
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘আমার প্রিয় বন্ধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যা আদেশ করেছেন আমি যেন নেতার অনুগত থাকি যদি তিনি বিকলাঙ্গ হন তথাপি। (মুসলিম)
হযরত উম্মে হাসীন (রাযি.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের খুতবা দেওয়ার সময় বলতে শুনেছি- ‘যদি কোন দাসকেও নেতা বানিয়ে দেয়া হয় আর সে আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে তোমাদিগকে পরিচালনা করে তোমরা তার অনুগত থাকবে। (মুসলিম)
অতএব প্রমাণ হলো যে, নেতৃত্বের কোন আচরণ পছন্দ হোক আর না হোক, তার সামাজিক অবস্থান যাই হোক তার আনুগত্য করতে হবে। শরয়ী কারণ ছাড়া আনুগত্য প্রত্যাহার করা যাবে না।
নেতৃত্বের আনুগত্য শুধু শরীয়তসম্মত কাজে
নেতৃত্বের আনুগত্য জরুরি। কিন্তু তা শর্তহীন নয়। আনুগত্য শুধু শরীয়ত-সম্মত আদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন গোনাহ বা অন্যায় কাজে আনুগত্য নেই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:
وتَعَاوَنُوا عَلَى البر والتقوى - وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثم والعدوان.
‘পুণ্যময় ও তাকওয়ামূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করো না।’ (সূরা মায়েদা : আয়াত ২)
আর আনুগত্য মানে নেতৃত্বের কাজের সহযোগিতা। অতএব যা পাপমূলক, অন্যায় তাতে আনুগত্য চলবে না। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.
‘স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা চলবে না।’ (শরহে সুন্নাহ)
لا طَاعَةٌ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المعروف.
‘নাফরমানীর ব্যাপারে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল মারূফ তথা ন্যায়সঙ্গত ও শরীয়তসম্মত কাজে।’ (বুখারী-মুসলিম)
السمعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ فَلَا سَمَعَ ولا طاعة.
‘গোনাহের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নেতার আদেশ শ্রবণ ও আনুগত্য প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। গোনাহের নির্দেশ দেয়া হলে তার কথা শোনাও যাবে না, আনুগত্য করা যাবে না।’ (বুখারী)
উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট হলো গোনাহ ও অন্যায় কাজে কোন আনুগত্য করা চলবে না। শুধু শরীয়তসম্মত কাজেই নেতৃত্ব-আনুগত্য পাওয়ার হকদার।
প্রসঙ্গত একটি কথা বলা দরকার যে, যদি নেতৃত্ব বা সংগঠনের পক্ষ থেকে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হয় যা শরীয়তের সুস্পষ্ট ও ঐকমত্যের খেলাফ না হয়। কিন্তু কেউ কেউ হয়ত তাকে সঙ্গত মনে করে না বা বিষয়টি বিরোধপূর্ণ, যাতে বিভিন্ন মতের অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব বা সংগঠনের সাথে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকলেও আনুগত্য প্রত্যাহারের কোন অবকাশ নেই।
অনেকের ধারণা, আনুগত্য সংক্রান্ত নির্দেশগুলো শুধু রাষ্ট্রীয় বৈধ শাসকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সংগঠন বা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক বা সরকারের আনুগত্য দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্যই জরুরি। কেউ তাকে অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু বিশেষ কোন দ্বীনি সংগঠনের নেতৃত্বের আনুগত্য করতে দেশের সব মানুষ আইনত বাধ্য নয়। তবে যদি কোন সংগঠনে কেউ যোগদান করে তাহলে সে সংগঠনের নেতৃত্বের আনুগত্য তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। যে সমস্ত লোকেরা বা তাদের বিধিসম্মত প্রতিনিধিরা যাকে বা যাদেরকে দ্বীনি সংগঠন বা দ্বীনি আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে সেই নেতৃত্বের বা সংগঠনের আনুগত্য করতে হবে। কোন শরয়ী বা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে তিনি সংগঠন পরিত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি সংগঠনের অধীনে থাকবেন এবং সংগঠনের কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত শরীয়তের সুস্পষ্ট খেলাফ না হবে ততক্ষণ অবশ্যই তাকে আনুগত্য করে যেতে হবে।
অনেক সময় দেখা যায় কারো বিবেচনায় কোন অনুপযুক্ত বা অযোগ্য কেউ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অথবা ব্যক্তিগতভাবে তাকে হয়ত তিনি পছন্দ করেন না। এজন্যই তিনি আনুগত্য করতে শিথিলতার আশ্রয় নেন। ইসলামী শরীয়তে কিন্তু এ ধরনের মনোভাব ও প্রবণতার সুযোগ নেই।
প্রসঙ্গত এটাও জানা দরকার যে, শৃঙ্খলা সংরক্ষণও এতায়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোন দ্বীনি সংগঠনের গঠনতন্ত্র বর্ণিত নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রণীত সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে চলাও এতায়াত বা আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সত্যিকার আনুগত্য তখন হবে যখন নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ও গঠনতান্ত্রিক নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।
অনেকের ধারণা গঠনতন্ত্র কোন কুরআন-হাদীস নয়। তাই তাকে ইচ্ছে মত লঙ্ঘন বা পরিহার করা যেতে পারে। এ ধারণা ঠিক নয়। অবশ্যই গঠনতন্ত্র, কুরআন-হাদীস নয়, তবে কুরআন-হাদীসের বিধান কায়েমের লক্ষ্যে কুরআন-হাদীসকে সামনে রেখেই গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই সংগঠনে থাকতে হলে গঠনতন্ত্র মেনে চলতে হবে। গঠনতন্ত্রের কোন বিষয় সঠিক বা কল্যাণকর মনে না হলে যথানিয়মে তাকে সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত অবশ্যই গঠনতন্ত্র মেনে চলতে হবে। একে হালকা করে দেখার কোন শরয়ী সুযোগ নেই।
আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য
যিনি নির্দেশ দেবেন, যিনি দায়িত্বশীল তাঁকে আদেশ দান ও আনুগত্যের প্রশ্নে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে:
১. সংগঠনের দায়িত্বশীল হিসেবে তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, তাঁর অবস্থান বা পজিশন সমস্ত মুসলমানদের বা কোন দেশের মুসলমানদের প্রধান নেতৃত্ব বা শাসকের মতো নয়। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বা শাসকের নির্দেশ দানের অধিকার সবার উপর এবং শরীয়তের সীমানায় সবাই তাঁর বা তাঁদের নির্দেশ মানতে বাধ্য। কিন্তু সংগঠনের নেতৃত্বের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত লোকদের জন্যই প্রযোজ্য। বাইরের লোকদের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়। বাইরের লোকদের তা মানার ব্যাপারটা স্বেচ্ছামূলক। কাজেই সংগঠনের নেতৃত্ব যদি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব বা শাসকের মতো ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে বসেন তাহলে তা হবে মারাত্মক ভ্রান্তি। এরূপ মনোভাব থাকলে আদেশ দানের ক্ষেত্রে রয়েছে সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা।
মনে রাখা দরকার সংগঠনের নেতৃত্বের ক্ষমতা ও অধিকার সংগঠনের গঠনতন্ত্র দ্বারা বা সংগঠনের স্বীকৃতি
নীতিমালা ও বিধি-বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর ভেতরেই থেকে নির্দেশ দিতে হবে।
২. সংগঠনের নেতৃত্বের ক্ষমতা ও অধিকার আন্দোলন এবং সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কর্মীদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণের তিনি অধিকারী নন। তবে সংগঠনের ও আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন হলে তিনি কোন কর্মীর ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বটে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যক্তির সামর্থ্য ও অধিকারের পরিপন্থী হতে পারবে না। তবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যা সংগঠনের ও আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় সেক্ষেত্রে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে কিন্তু বাধ্য করা যেতে পারে না। শরীয়ত যে সমস্ত ব্যক্তিগত অধিকার দিয়েছে সংগঠন কেন সাধারণভাবে তাতে রাষ্ট্রেরও হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। তবেব পরিকল্পনা ও পরামর্শ দান করা যেতে পারে।
৩. কর্মীদের দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই তার সামর্থ্যের বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন কিছু বিবেচনা না করে দায়িত্ব চাপানো চলবে না। কঠিন দায়িত্ব দিতে হলে অবশ্যই তাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন:
السمع والطاعة نا إِذَا بَابَعنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُم. الله عليه وسلم على الله
‘যখনই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করতাম তখন তিনি বলতেন, যা তোমাদের সাধ্যমত হয়।’ (মুসলিম, বুখারী)
যেখানে রাসূলের নিকট বায়আতের ক্ষেত্রেও সাধ্যমত শর্ত ছিলো সেখানে অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও তো তা আরো বেশি প্রযোজ্য। অতএব সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আদেশ দিতে হবে, দায়িত্ব দিতে হবে।
৪. সংগঠনের আমীর বা পরিচালকমণ্ডলীকে একথাও বুঝতে হবে যে, তার নির্দেশ কার্যকর করার জন্য কোন শক্তি প্রয়োগের অধিকারী তিনি নন। তাই অনুপ্রেরণা ও দ্বীনি চেতনার সৃষ্টি এবং নৈতিক শক্তি ও আবেদনের মাধ্যমেই নির্দেশ কার্যকর ও বাস্তবায়িত করতে হবে।
অতএব সংগঠনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগের বা অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। এখানে নৈতিক শক্তিই মূখ্য, আইনের শক্তি নয়। অবশ্য গঠনতন্ত্র বা বিধিবদ্ধ নিয়ম-শৃঙ্খলাও একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করে।
বস্তুত আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা প্রয়োজন। যিনি আদেশ দিবেন তিনি শরীয়ত ও গঠনতন্ত্রের সীমানার মধ্যে আদেশ দিবেন, আর যাদেরকে আদেশ/নির্দেশ দেয়া হবে শরীয়ত ও গঠনতন্ত্র বিরোধী না হলে আন্তরিকতা, দ্বীনদারী ও আমানতদারীর সাথে তারা সে নির্দেশ পালন করবেন। তাহলে সুশৃঙ্খলভাবে ও শরীয়তমাফিক সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালিত হবে।
শূরায়ী ব্যবস্থা
একটি ইসলামী সংগঠনে শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদী সম্পাদন ও পরিচালনা, মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শ বা শূরায়ী পদ্ধতি অত্যাবশ্যক। বস্তুত শূরা ইসলামী ব্যবস্থার অন্যতম মৌল বিষয়।
শূরার গুরুত্ব
১. ‘শূরা’ ইসলামী সমাজের অন্যতম মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত: মক্কায় যখন ইসলাম ও মুসলিম সমাজ গঠনের মূলনীতি পেশ করা হচ্ছিল তখনই ‘শূরার’ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে:
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصلوة وأمرهم شورى بينهم وَمِمَّا ولة على ٥٧ الدر رزقنهم ينفقون.
‘আর যারা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে, যাদের কার্যাদী পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং আমরা রিযিক বাবদ যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে...।’ (সূরা শূরা: আয়াত ৩৮)
উপরের আয়াতটি মক্কী যুগের। মক্কী যুগে ইসলামের মূলনীতিগুলো পেশ করা হচ্ছিল। তাছাড়া পরামর্শকে আল্লাহর প্রতি সাড়া দেয়া, নামায কায়েম করা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়- পরামর্শ ব্যবস্থা ইসলামে কত গুরুত্বপূর্ণ।
২. পরামর্শ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সরাসরি নির্দেশ:
مل وشاورهم في الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ.
‘এবং তুমি তাদের সঙ্গে সামষ্টিক বিষয়াদি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ কর। যখন সংকল্প গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে।’ (সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১৫৯)
উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ওহুদ যুদ্ধের পর। ওহুদ যুদ্ধের আগে মহানবী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। পরামর্শের বিষয় ছিলো মদীনায় থেকে শত্রুদের মোকাবেলা করা হবে না, শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করা হবে। সাধারণভাবে সাহাবীগণ বিশেষভাবে তরুণ সাহাবীগণ শহরের বাইরে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মতকে মেনে নিয়ে মদীনার বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মদীনায় থাকার দিকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোভাব বেশি ছিল। কিন্তু তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেন। ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যয় হয়। এরূপ বিপর্যয়কর পরিণতি হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাআলা পরামর্শ করার উপর তাগিদ করেছেন। অর্থাৎ পরিণতি যাই হোক পরামর্শ করার নীতি অব্যাহত রাখতে হবে। কোন ক্ষেত্রে বিপর্যয় বা মর্মান্তিক পরিণতি দেখা দিলেও পরামর্শের নীতি পরিহার করা চলবে না। কাজেই পরামর্শ নীতি যে ইসলামে কত গুরুত্বপূর্ণ তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
৩. পরামর্শভিত্তিক সমাজই বাসযোগ্য ও কল্যাণকর সমাজ: মুসলমানদের জন্য যে সমাজ বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সমাজের কার্যাদি পরামর্শভিত্তিক সম্পন্ন হবে। যেমন হাদীসে আছে:
اذا كان امرئكم خياركم واغنيائكم سمحانكم و اموركم شوری بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها.
‘যখন তোমাদের নেতারা হবে ভালো মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং সামগ্রিক কাজকর্ম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নিচের ভাগ থেকে উত্তম হবে।’ (তিরমিযী)
৪. পরামর্শ ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র তথা খেলাফত হতে পারে না: হযরত ওমর (রাযি.) বলেছেন-
لا خلافة الا عن مشورة
‘পরামর্শ ছাড়া খেলাফত হতে পারে না।’ (কানযুল উম্মাল)
৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং পরামর্শ করতেন: ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন, বিশেষভাবে ঐসব ব্যাপারে যেসব বিষয়ে কোন ওহীর নির্দেশ ছিল না।
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেছেন, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে যাবতীয় ব্যাপারে কাউকেও অধিকতর পরামর্শ করতে দেখেননি। (তিরমিযী, বায়হাকী)
পরবর্তী সত্যপন্থী খলীফাগণও একই নীতি অনুসরণ করতেন। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত আবু বকর (রাযি.) কোন সমস্যার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর কোন সমাধান পেতেন না তখন সমাজের আলেম ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ডেকে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। (দ্রষ্টব্য: সুনান আল-কুবরা: খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫)
হযরত ওমর (রাযি.) ও অন্যান্য খলীফাগণও তাই করতেন।
৬. পরামর্শের প্রশ্নে ফকীহগণের মতামত ইতিবাচক: ইবনে আতিয়্যা বলেন, পরামর্শ হলো শরীয়তের মূলনীতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যে আমীর পরামর্শ নেবেন না তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব। এতে মতবিরোধ নেই। (বাহরুল মুহিত, আবু হুয়ান)
ইবনে কাসীরের মতে পরামর্শ হচ্ছে ওয়াজিব। ইবনে তাইমিয়া বলেন-’আমীরের পরামর্শ ছাড়া কোন উপায় নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার ন্যায় মহান ব্যক্তির প্রতি যখন এই নির্দেশ তখন অন্যদের ক্ষেত্রে তো আরো অধিক প্রযোজ্য। (আস-সিয়াসাতুশ শরীয়াহ)
অতএব স্পষ্ট হলো যে শূরা হচ্ছে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠন পরিচালনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। শূরা ছাড়া ইসলামী আন্দোলন, সংগঠনও চলতে পারে না।
এখন প্রশ্ন- পরামর্শ শুধু করাই হবে না তা মানতেও হবে। এ পর্যায়ে ইবনে কাসীর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন: ‘ইবনে মারদুবিয়া হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে فيذا । বা দৃঢ় সংকল্পের তাৎপর্য সম্পর্কে عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন: العزم
مشورة اهل الرى ثم اتباعهم.
অর্থাৎ মত দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা এবং পরে পরামর্শ মেনে নেয়া বা তার অনুসরণ করা।’ (তাফসীরে ইবনে কাসীর সূরা আলে-ইমরান, ১৫৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)
অতএব স্পষ্ট হল- পরামর্শ করা এবং পরামর্শক্রমে সর্বসম্মত বা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাই কার্যকর করতে হবে। তাছাড়া এর দাবিও হচ্ছে শুধু পরামর্শ করা নয় বরং পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য সম্পন্ন করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ করার পর নিজের মত পরিহার করে অধিকাংশ সাহাবীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। (ইউসুফ কারযাভী: আল-ফিকহুয যাকাত, খণ্ড ২, পরিচ্ছেদ ৭)
وأمرهم شورى بينهم
খোলাফায়ে রাশেদীনের ঐতিহ্যও এ মতের অনুকূল।
বর্তমান যুগে একটি ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পলিসি নির্ধারণ ইত্যাদির জন্য বিধিবদ্ধ একটি মজলিসে শূরা থাকে। আবার কেন্দ্রীয় সংগঠনের আওতায় শাখা সংগঠনেও মজলিসে শূরা থাকে। সংগঠনের গঠনতন্ত্রে সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরার গঠন, ক্ষমতা, বৈঠক অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ থাকে। সংগঠনের নেতৃত্বকে যথাযথভাবে শরীয়ত মাফিক ও গঠনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী শূরায়ী পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে। শূরাকে এড়িয়ে কোন স্বেচ্ছাচারিতা ও ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে নেই। আমীরের দায়িত্ব হচ্ছে যথাযথভাবে শূরায়ী ব্যবস্থা কার্যকর করা।
মজলিশে শূরার সদস্যদের দায়িত্ব
অন্য দিকে যারা শূরার সদস্য হবেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পুরোপুরি আমানত-দারী সহকারে নিজের জ্ঞানমত সঠিক পরামর্শ দেওয়া। পরামর্শ দান প্রসঙ্গে একটি হাদীসে আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
والمستشار مؤتمن اذا أستشير فليشره بما هو صانع لنفسه.
‘যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে হলো আমানতদার। কাজেই সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যকে তাই পরামর্শ দিবে।’ (মুজামে আওসাত গ্রন্থে আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, মাযহারী)
আর একটি হাদীসে আছে, হযরত জাকের (রাযি.) থেকে বর্ণিত- ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তোমার কোন ভাই যদি তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে আসে, তবে তাকে সত্য পরামর্শ দান কর।’ (তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত)
কাজেই পরামর্শ সভা বা মজলিসে শূরার সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে আমানত মনে করে ঈমানদারীর সাথে নিজের জ্ঞান ও বিবেক অনুযায়ী মতামত ব্যক্ত করতে হবে। অবহেলা করা, ব্যক্তি বা উপদলীয় স্বার্থে সঠিক পরামর্শ দানে বিরত থাকা খেয়ানতের শামিল। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।
মজলিসে শূরার বৈঠকের আলোচনার গোপনীয়তা সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মজলিসে শূরা বা যে কোন বৈঠকের আলোচনা সংগঠনের সিদ্ধান্ত ছাড়া বাইরে প্রকাশ করা, নিয়ম-বহির্ভূত পন্থায় বা অসংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট বলাও অত্যন্ত অসংগত। কেননা বৈঠকের আলোচনাও মতামত।
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
المجالس بالامانة.
‘বৈঠকসমূহের আলোচনা আমানত স্বরূপ।’ (আবু দাউদ)
অতএব বৈঠকসমূহের আলোচনা বিধি-বহির্ভূত পন্থায় বাইরে প্রকাশ করা খেয়ানতের শামিল। এ পর্যায়ে আরো একটি বিষয়ও গুরুত্বের দাবিদার। শূরার সদস্যগণ নিজের মতামত দেবেন, পরামর্শ দেবেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই নিজের মতামত মানাবার জন্য জিদ ধরবেন না। নিজের মতের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে হবে। কোন কারণে সামষ্টিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে না পারলেও গৃহীত সিদ্ধান্তকেই কার্যকর করতে হবে। এর অন্যথা করা যাবে না। গৃহীত সিদ্ধান্ত ভুল মনে করলেও তা যদি শরীয়তের সুস্পষ্ট খেলাফ না হয়, তাহলে নিজের মত নিজের মধ্যে রেখেই গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে। নিজের মতে সিদ্ধান্ত না হলে যদি কেউ আনুগত্য করতে বা মানতে অনীহা দেখায় বা শূরার বাইরে প্রকাশ করে বেড়ায় তাহলে তা নিয়ম-শৃঙ্খলার খেলাফ এবং আত্মম্ভরিতার লক্ষণ। এ ধরনের প্রবণতা ও মনোবৃত্তি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। তা না হলে কোন সংগঠন ও আন্দোলন সুষ্ঠভাবে চলা সম্ভব নয়।
সদস্যমণ্ডলী তথা কর্মীবাহিনী
একটি ইকামতে দ্বীনের সংগঠনের জন্য তার সদস্যগণ ও কর্মীবাহিনী অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সদস্য-কর্মীদের মানের উপর নির্ভর করে সংগঠনের মান। কর্মীদের সামগ্রিক যোগ্যতা ও গুণপনার উপর নির্ভর করে সংগঠনের সাফল্য। তাই দ্বীনি সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে কাম্য ও প্রয়োজনীয় গুণের সমাবেশ ঘটা জরুরি। মানসম্পন্ন কর্মী ছাড়া আন্দোলন ও সংগঠন অগ্রসর হতে পারে না। নিম্নে আন্দোলনের কর্মীদের ব্যক্তিগত পর্যায়ের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর উপর আলোকপাত করা হলো।
কর্মীদের গুণাবলী
ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীকে যথাযথভাবে দ্বীনি কর্তব্য আঞ্জাম দেওয়ার জন্য, ঠিকমত ভূমিকা পালনের জন্য, কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য বিভিন্নমুখী গুণাবলীর প্রয়োজন। প্রতিটি সৎগুণই কর্মীর মানকে উন্নত করবে, কর্মীদের জন্য সহায়ক হবে। তবে কতগুলো এমন গুণ রয়েছে যা দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হচ্ছে এমন মৌলিক গুণ যা ছাড়া একজন কর্মী যথার্থভাবে কর্মী হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। এসব মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে:
১. দ্বীনের যথার্থ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান: দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীগণ দ্বীনের জন্য কর্মরত। যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন সে দ্বীন সম্পর্কে একজন কর্মীর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান থাকতে হবে। শরীয়তের সীমা সম্পর্কে তাকে অবগত হতে হবে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য তাকে বুঝতে হবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যান্য মতামত ও আদর্শের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার মত জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হবে। সংগঠন ও আন্দোলন সম্পর্কেও তার পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মোটকথা দ্বীন, আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে তার পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। জ্ঞান অর্জন ছাড়া ভাল কর্মী হওয়া সম্ভব নয়।
২. দ্বীনের প্রতি অবিচল-অটুট আস্থা ও ঈমান: ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর দ্বীনের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। শুধু সাদামাটা ঈমান নয় বরং তার ঈমানের গভীরতা থাকতে হবে। যে কোন মতবাদের চেয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে কল্যাণকর এ বিশ্বাস ও আস্থা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকতে হবে। মানসিক প্রশান্তি না থাকলে কোন আন্দোলনের জন্য কাজ করা যায় না। দোদুল্যমানতা নিয়ে কাজ চলে না। তাই দ্বীনি আন্দোলনের একজন কর্মীকে আল্লাহর প্রতি, তাঁর মহান গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে। আখেরাতের প্রতি অটল ঈমান রাখতে হবে। কুরআন-হাদীসে আখেরাতের চিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথই একমাত্র সঠিক সত্য পথ। তার বিরোধী বা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সমস্ত মত-পথ সবই ভ্রান্ত। মোটকথা দৃঢ় ও অবিচল ঈমান ছাড়া দ্বীনি আন্দোলনের যথার্থ কর্মী হওয়া যায় না।
৩. কথা ও কাজে মিল: একজন কর্মীকে অবশ্যই কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। তিনি যা বিশ্বাস করেন এবং বলেন, আমল ও কাজও তার সেরূপ হওয়া চাই। যে বিষয়কে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন যা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি শরীক হয়েছেন তাঁর জীবনে, আচার-আচরণে, আমল-আখলাকে তা বাস্তবায়িত হতে হবে। যাকে মিথ্যা বলে জানেন, ভুল ও ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন তিনি যদি নিজেকে এসব থেকে দূরে রাখতে না পারেন তাহলে তাঁর পক্ষে দ্বীনি আন্দোলনে যথার্থ ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। কথা ও কাজে যার মিল নেই তার দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কথা ও কাজের মিল, চরিত্র ও কর্মের সাদৃশ্য সৃষ্টির জন্য একজন কর্মীকে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
৪. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক: একজন দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীর বড় সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাঁর যথার্থ সম্পর্ক। আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে দ্বীনি আন্দোলনের পথে বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না। দ্বীনি আন্দোলন আল্লাহ আন্দোলন। দ্বীনি আন্দোলনের কর্মী আল্লাহর কর্মী। তারা আল্লাহর দলের (হিজবুল্লাহর) সদস্য। তাঁরা আল্লাহর সৈনিক। কাজেই আল্লাহর সাথে যথার্থ ও গভীর সম্পর্ক ছাড়া আল্লাহর দলের ‘প্রকৃত কর্মী’ হওয়া যায় না।
৫. চরিত্র মাধুর্য: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে তাদের চরিত্র মাধুর্য। উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা কুরআন-সুন্নাহয় বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। আল-কুরআন স্পষ্ট বলেছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
‘হে নবী! আপনি মহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।’ (সূরা কলাম: আয়াত ৪)
হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে-’আমাকে চরিত্র পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।’ (মালেক)
* কর্মীদের গুণাবলীর বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের ‘আদর্শ কর্মী’ বইটি দ্রষ্টব্য।
কাজেই উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ইসলামে অত্যন্ত বেশি। বিশেষ করে যিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবেন, যিনি দ্বীনের পথে সংগ্রাম করেন, ন্যায়ের আদেশ করেন ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার কাজ করেন, যিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালাবেন তাকে অবশ্যই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।
আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের বিশাল হৃদয় থাকা চাই। তাদের হতে হবে উদার মনের অধিকারী। তারা হবেন মানব প্রেমিক। মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা তাদের থাকা জরুরি। তারা হবেন ভদ্র, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আত্মনির্ভরশীল, মিষ্টভাষী, কষ্টসহিষ্ণু ও সদালাপী, তারা হবেন বিশ্বস্ত, আমানতদার, ইনসাফগার। তারা হবেন সেবাপরায়ণ, ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল। যাবতীয় উত্তম গুণের তারা হবেন আঁধার। একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা মৌলিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:
امرني ربي بنشع (۱) خَشْيَةِ اللهِ فِي السَّرَ وَالْعَلَانِيَّةِ (۲) وكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا (۳) وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا くて、 (٤) وان اصل من قطعتي (٥) وَاعْطِي مَنْ حَرمني (১) وَاعْفُو مَنْ ظَلَمَنِي وأن (۷) يكون صمته صينى فكرا (۸) ونطقى ذكرا (۹) ونظرى عبرة
أنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.
‘আমার রব আমাকে নয়টি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন:
১. প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় যেন আল্লাহকে ভয় করি।.
২. ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় যেন ইনসাফের কথা বলি।
৩. দারিদ্র্য ও বিত্তশালীতা যে কোন অবস্থায়ই যেন সততা ও মধ্যম পন্থার উপর কায়েম থাকি।
৪. যে আমার থেকে কেটে গেছে তাকে যেন জুড়ে নেই।
৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে তাকে যেন দান করি।
৬. আমার উপর যে জুলুম করে তাকে যেন মাফ করি।
৭. আমার নিরবতা যেন চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়।
৮. আমার কথাবার্তা যেন খোদার স্মরণমূলকক হয়।
৯. এবং আমার দৃষ্টি যেন উপদেশ গ্রহণের সৃষ্টি হয়।
এসব গুণাবলী উল্লেখ করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সৎকাজে আদেশ দেবার এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার।’ (মেশকাত, রাযিন ভয় ও কান্না অধ্যায়])
অতএব দ্বীনি আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে মহান চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক
ইসলামী সমাজে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলন ও পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক সম্পর্ক আন্দোলন ও সংগঠনের একটি মৌলিক বিষয়। তাই ইসলাম এ সম্পর্কের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে।
পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি
কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ সম্পর্ক হবে ভ্রাতৃত্বের, বন্ধুত্বের ও ভালোবাসার। একজন কর্মী হবে আরেকজন কর্মীর ভাই, বন্ধু ও ভালোবাসার পাত্র। (অবশ্য এ সম্পর্ক সমস্ত মুমিনদের জন্যই প্রযোজ্য।)
ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক
আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সম্পর্ককে মৌলিকভাবে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআনের ভাষায়:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أخوة
‘মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।’ (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১০)
অর্থাৎ একজন আপন ভাইয়ের সঙ্গে মানুষ যে সম্পর্ক রাখে, যে মানসিক টান অনুভব করে, দ্বীনের সহযাত্রীদের সাথেও সে সম্পর্কই রাখতে হবে। একজন মুমিন, একজন কর্মী আরেকজন কর্মীর ভাই মনে করবে, তার সাথে ভাইয়ের মতো ব্যবহার করবে এর চেয়ে উত্তম সম্পর্ক আর কি হতে পারে?
কর্মীদের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বের, পৃষ্ঠপোষকতার
কুরআনুল কারীমে কর্মীদের সম্পর্ককে বেলায়েত-বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক বলে আখ্যায়িত করেছেন। একজন দ্বীনি আন্দোলনের কর্মী হবে আরেক কর্মীর ওলি, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। কুরআনের ভাষায়:
ارم امنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أووا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ.
‘যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর ওলি-বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।’ (সূরা আনফাল: আয়াত ৭২)
অর্থাৎ দ্বীনের সাথে সংগ্রামকারীদের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বের ও পৃষ্ঠপোষকতার।
ভালোবাসার সম্পর্ক
যারা মুমিন তাদের সম্পর্কের ধরণটাই হবে ভালোবাসার। তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে এমন সম্পর্ক যেখানে প্রেম ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে মুমিনগণ। বিশেষ করে দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীগণ। এ হচ্ছে খোদ ঈমানের দাবি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়:
لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا.
‘তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।’ (মুসলিম)
আর আল্লাহ তাআলার অসীম অনুগ্রহের কারণেই এ ধরনের ভালোবাসার বন্ধন সম্ভব, কোন বৈষয়িক শক্তিবলে নয়-
ي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. والف بين قلوبهم - لو أنفقت ما في الأرض :
‘মুমিনদের হৃদয়কে পরস্পর জুড়ে দিয়েছেন। যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও ব্যয় করতে তাহলেও লোকদের মন পরস্পর জুড়ে দিতে পারতে না, তাদের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না।’ (সূরা আনফাল: আয়াত ৬৩)
كرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِن كنتم هم آن ডব ংড়হমং, এঙঠ এঁ اعداء فالف بين قلوبكم
فَاصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا .
‘আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করা যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে। আল্লাহ তোমাদের মন মিলিয়ে দিয়েছেন-ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তারই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।’ (সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১০৩)
দয়া-কোমলতার সম্পর্ক
মুমিনদের পরস্পর সম্পর্ক বুঝানোর জন্য পবিত্র কুরআন রহমত() শব্দটি ব্যবহার করেছেন:
رحماء بينهم.
‘(মুমিনদের) পরস্পর রহমদিল।’ (সূরা ফাতহ: আয়াত ২৯) অর্থাৎ তাদের সম্পর্ক হবে রহমতের তথা দয়া-কোমলতার সাথে সম্পর্ক।
আল্লাহর পথে সংগ্রাম রত মুমিনদের সম্পর্ক হবে সীসাঢালা প্রাচীরের মত:
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِهِ صَفًّا كَانَهم بنيان مرصوص.
‘আল্লাহ তো তাদেরই ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে।’ (সূরা সফ: আয়াত ৪)
এ প্রসঙ্গে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
يشد بعضه بعضا . المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
‘এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাচীর বা গৃহের মতো। যার একাংশ আরেক অংশকে সুদৃঢ় রাখে।’ (বুখারী-মুসলিম)
মুসলমানরা পরস্পর দেহের মতো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَطَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشتكى عضوا تداعى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِاشْهَرِ الْحُمى.
‘তুমি ঈমানদারগণকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র রজনী ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।’ (বুখারী-মুসলিম)
মুমিনরা বিশেষ করে ঈমানের দাবি পূরণকারীরা তথা দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীরা হবে এক দেহের মতো। আর একটি হাদীসে আছে:
به اشتكى كله وإن اشتكى رأسه عينه الْمُؤْمِنُ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِن اشْتَى عَ اشتكى كله
‘সকল মুমিন একজন ব্যক্তির মতো। যদি তার চোখ অসুস্থ হয় তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদি তার মাথা ব্যথা হয় তখন তার সর্বাঙ্গই অসুস্থ হয়ে পড়ে।’ (মুসলিম)
উপরোক্ত আলোচনা থেকে কর্মীদের প্রকৃতি ও রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর্মীদের সম্পর্ক হবে ভ্রাতৃত্বের, বন্ধুত্বের, ভালোবাসার ও রহমতের। কর্মীরা হবে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সম্পর্কযুক্ত। তারা হবে একটি দেহের মতো, তারা হবে একই ব্যক্তির মতো। বস্তুত সুদৃঢ় সম্পর্ক ও একাত্মতা আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অপরিহার্য।
ভ্রাতৃত্ব বা সম্পর্কের গুরুত্ব
মুমিন ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ঈমানের দাবি পূরণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আখেরাতের পুরস্কার লাভ, আন্দোলনের সফলতা অর্জন ইত্যাদি সর্বদিক দিয়েই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব অপরিহার্য। কুরআন-সুন্নাহয় এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে:
ক. ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব-ভালোবাসা ঈমানের অনিবার্য দাবি-
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخوة
‘মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।’ (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১০) অতএব সত্যিকার মুমিন হতে হলে পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে।
لا تؤمنوا حتى تحابوا.
‘তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে।’ (মুসলিম)
খ. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর সম্পর্ক-ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা প্রয়োজন: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
ور وجبت محبتي للمتحابين في المتجالسين في قَالَ الله تَعَالَى وَجَبَتْ مُحَتى لا ور المتزورين في والمتبادلين في.
‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আমার জন্য পরস্পর ভালোবাসে, আমার জন্য একত্রে উপবেশন করে, আমার জন্য পরস্পর সাক্ষাত করতে যায় এবং আমার জন্য পরস্পরের সাথে অর্থ ব্যয় করে তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা অনিবার্য।’ (মালিক)
গ. আখেরাতের প্রভূত পুরস্কারের ঘোষণা: হাদীসে আছে- আল্লাহ তাআলা তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন:
الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنور يَغْبِطُهُمُ النَّبيُّونَ وَالشُّهَدَاء
‘যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে পরস্পরকে ভালোবাসবে তাদের নুরের মিম্বর তৈরি হবে এবং নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন।’ (তিরমিযী)
যে সাত শ্রেণীর লোক হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে:
رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.
‘দুইজন যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবেসেছে, তারই জন্য একত্রিত হয়েছে এবং একই খাতিরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।’
ঘ. ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব অপরিহার্য: ইসলামী আন্দোলনকে সফল করার জন্য, প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্য পারস্পরিক মজবুত সম্পর্ক, ভালোবাসা, সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজন। বন্ধুত্ব ও মজবুত সম্পর্কের পরিবর্তে যদি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে, আল্লাহর পথের মুজাহিদদের মধ্যে ঝগড়া-বিরোধ-বিভেদ সৃষ্টি হয় তাহলে সফলতার আশা অত্যন্ত দুরূহ। এজন্যই স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করলে যে মন্দ পরিণতি হয় তা উল্লেখ সহকারে এ থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে বলেছেন:
تنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ. الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَ واطيعوا الله ورسو
‘আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে।’ (সূরা আনফাল: আয়াত ৪৬)
অতএব ঝগড়া-বিবাদের বিপরীত মজবুত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কই সফলতার সোপান। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা কুফরী শক্তির পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার উদাহরণ পেশ করে বলেছেন যে, মুসলমানরা যদি একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় এগিয়ে না আসে তাহলে কুফরী শক্তির প্রাধান্যের কারণে যমীনে মারাত্মক ফেতনা ও কঠিন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي وفساد كبير. فتنة في الأرض
‘আর যারা কাফের তারা পরস্পর সহযোগী বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। তোমরা (হে ঈমানদার লোকেরা) যদি এমন ব্যবস্থা না কর (পরস্পর সাহায্যে এগিয়ে না আসো) তাহলে যমীনে বড়ই ফেতনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।’ (সূরা আনফাল: আয়াত ৭৩)
অতএব ফেতনা-ফাসাদ প্রতিরোধ, মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য মুসলমানদের-মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক হতে হবে অত্যন্ত মজবুত ও পৃষ্ঠপোষকতর। পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত না হলে, পরস্পর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক না হলে প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় সফলতা আশা করা যায় না।
অতএব দ্বীনি কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। যথার্থ পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া দ্বীনি উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় না। এজন্যই দ্বীনি আন্দোলনে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর খুবই গুরুত্বারোপ করতে হবে।
পারস্পরিক সম্পর্কের মৌল ভিত্তি
মুমিনদের বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চারটি বিষয় রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমেই সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে। সেগুলো হচ্ছে-
১. কল্যাণ কামনা,
২. আদল বা সুবিচার,
৩. ইহসান বা সদাচারণ,
৪. ইছার বা অগ্রাধিকার।
উপরোক্ত চারটি গুণ মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, রক্ষা করা ও বিকশিত করার জন্য অপরিহার্য। এজন্য কুরআন-হাদীসে এ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
কল্যাণ কামনা
কল্যাণ কামনা বা নসিহত অত্যন্ত মৌলিক বিষয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
الدِّينُ النَّصِيحَةُ (ثلاثا)
‘দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা।’ (মুসলিম)
অপর হাদীসে আছে:
وَالَّذِي نَفْسِي بَيدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدِ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.
‘যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তার শপথ। কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য’যা পছন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে।’ (বুখারী-মুসলিম)
এজন্য মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ.
‘সে তার ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে সে অনুপস্থিত থাকুক আর উপস্থিত।’ (নাসায়ী)
অতএব পারস্পরিক কল্যাণ কামনা অতীব প্রয়োজনীয় গুণ। এ গুণের অভাব থাকলে সত্যিকার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।
আদল বা সুবিচার
আদল বা সুবিচার হচ্ছে সামাজিক সুবিচারের ভিত্তি। যেখানে আদল নেই সেখানে কোনো ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। আদলের পাশাপাশি ইহসান বা সদাচরণও গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বয়ং আল্লাহ এ দুটো গুণ অর্জনের নির্দেশ দিচ্ছেন:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.
‘আল্লাহ তাআলা আদল ও ইহসানের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।’ (সূরা নাহল: আয়াত ৯০)
জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ইনসাফ করা, ন্যায়বিচার করা ইসলামের মৌলিক দাবি। সম্পর্ক রক্ষার জন্যই এটি অতীব জরুরি। যেখানে সুবিচার নেই, সেখানে কোন সুসম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্যই সর্বাবস্থায় আদেলের বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা বলা হয়েছে।
كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاء.
‘ক্রোধ অথবা সন্তুষ্টি যে কোন অবস্থায় আদেলের উপর কায়েম থাক।’
ইহসান বা সদাচরণ
সুসম্পর্কেল জন্যই ইহসান বা সদাচরণ অত্যন্ত মৌলিক। আদল বা সুবিচার সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে আর ইহসান সম্পর্ককে মাধুর্য ও পূর্ণতা দান করে। ইহসান হচ্ছে এমন সবাগুণাবলীর সমষ্টি যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভাল ব্যবহার, সহানুভূতিশীলতা, শুভাকাঙ্ক্ষা, শিষ্টাচার, খোশ-মেযাজ, সৌজন্যবোধ, দয়া-অনুগ্রহ, রহমদিল, সহমর্মিতা, অগ্রাধিকার দান ইত্যাদি। এসব গুণাবলীর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয়, পূর্ণতা লাভ করে।
ইছার বা অগ্রাধিকার
একজন মুমিন যখন মুমিনদের প্রতি সুবিচার করে না, তাঁর হক শুধু পুরোপুরি আদায় করে না, নিজে যা পছন্দ তাই শুধু তার ভাইয়ের জন্যই পছন্দ করে না বরং নিজের স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা, রুচি-চাহিদা ইত্যাদির উপর তাঁর ভাইয়ের প্রয়োজন, স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা, রুচি-স্বভাব-প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয় তখন তাঁকে বলা হয় ইছার বা অগ্রাধিকার দান। এ হচ্ছে অতীব মহান গুণ। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ গুণের উপস্থিতির প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন:
ويؤثرون على انفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
‘এবং তারা নিজেদের উপর অন্যান্যদের (প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে।’ (সূরা হাশর: আয়াত ৯)
এ গুণ যখন মানুষ অর্জন করে তখন পারস্পরিক সম্পর্কের সর্বোচ্চ স্তর অর্জিত হয়। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী-সাথীগণের ক্ষেত্রে হয়েছিল।
সম্পর্ক বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ
পারস্পরিক সম্পর্ককে সংরক্ষণ করতে হলে, তাকে উন্নত করতে হলে কিছু গুণ যেমন অর্জন ও অনুশীলন করা দরকার তেমনি কিছু ত্রুটি ও দোষ থেকে মুক্ত থাকা দরকার। এমন কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে যা পারস্পরিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করে দেয়, যা দূর না করলে সম্পর্ক উন্নত তো দূরের কথা, সম্পর্ক রক্ষাই করা যায় না। কুরআন-হাদীসে এসব দোষ-ত্রুটির কঠোর নিন্দা করা হয়েছে এবং মুমিনদেরকে এসব থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ ও উপদেশ দেয়া হয়েছে।
যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক এবং সাংগঠনিক জীবনের জন্ন অত্যন্ত মারাত্মক তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ হচ্ছে:
১. অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ,
২. জান-মাল-দেহের উপর হস্তক্ষেপ,
৩. কটু কথা ও গালাগাল,
৪. গীবত,
৫. চোগলখোরী,
৬. লজ্জা দেয়া,
৭. তুচ্ছ জ্ঞান করা,
৮. ছিদ্রান্বেষণ,
৯. ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস,
১০. নিকৃষ্ট অনুমান,
১১. অপবাদ দান,
১২. ক্ষতি সাধন,
১৩. মনোকষ্ট দেয়া,
১৪. ধোঁকা-প্রতারণা,
১৫. হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা।
এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:
অধিকারে হস্তক্ষেপ
প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট কতিপয় অধিকার রয়েছে। এসব অধিকার আল্লাহ প্রদত্ত। এসব অধিকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এসব অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার সীমা ঠিক করে দিয়েছেন। এসব সীমালঙ্ঘন করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে:
وجہ الله فَلَا تَعْتَدُوهَا - وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودًا تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ.
‘এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। অতএব একে লঙ্ঘন করো না, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সেই জালেম।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ২২৯)
যে ব্যক্তি কারো অধিকার নষ্ট করে তার জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
‘যে ব্যক্তি কসম খেয়ে কোন মুসলমানের হক মেরেছে আল্লাহ নিঃসন্দেহে তার জন্য জাহান্নামকে অনিবার্য ও জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।’ এজন্য প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
المسلم منْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
‘মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান কারো উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।’
দেহ-জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ
সাধারণভাবে মানুষের যত অধিকার রয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে প্রাণের নিরাপত্তা। ইসলামে প্রাণের নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ নিরাপত্তা যে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ কারো প্রাণের উপর যে হস্তক্ষেপ করে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাকের ঘোষণা:
وَمَنْ تَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি গযব বা লানত বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন কঠোরতম শাস্তি।’ (সূরা নিসা : আয়াত ৯৩)
কাজেই কারো প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ যে ভয়াবহ অপরাধ তা অতি স্পষ্ট। ঠিক তদ্রূপ কারো মাল-সম্পদের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপও নিষিদ্ধ।
আল্লাহ পাক বলেছেন:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكام.
‘তোমরা অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না, মানুষের সম্পদ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করো না।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ১৮৮)
কটুকথা ও গালাগাল
কটুকথা ও গালাগাল, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاظُ الْجَعْفِرِي
‘কোন কটু ভাষাভাষী ও বদ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ (আবু দাউদ, বায়হাকী)
অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:
وَسِبَابُ المسلم فسوق.
‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী...।’ (বুখারী-মুসলিম) অতএব কটু ভাষণ, অশ্লীল কথা ও গালাগাল থেকে বিরত থাকতে হবে।
গীবত
গীবত হচ্ছে অন্যতম মারাত্মক অপরাধ। কোন ব্যক্তির পেছনে তার দোষ-ত্রুটি চর্চার নাম গীবত। আল্লাহ গীবত করতে নিষেধ করেছেন। গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।
وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا - انْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكر هنطوه
‘কেউ কারো গীবত করো না। তোমরা কি কেউ আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? একে তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে।’ (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১২)
গীবত সর্বতোভাবে পরিহার করে চলতে হবে। কোন শরয়ী, আন্দোলনী বা যথার্থ প্রয়োজন ছাড়া পেছনে কারো দোষ উল্লেখ করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।
চোগলখোরী বা কুটনামী
ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অন্যের কানে লাগানোকে চোগলখোরী বা কুটনামী বলে। এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক।
হাদীসে আছে- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّام
‘চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ (বুখারী-মুসলিম)
অতএব প্রত্যেককে চোগলখোরী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।
লজ্জা দেয়া
সম্পর্ক নষ্টকারী, অন্যতম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে, কাউকে তার সাক্ষাতে বা অন্য লোকের সামনে কোন দোষ-ত্রুটির জন্য লজ্জা দেয়া। তাকে অবমাননা করা। এ অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। তাই এ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে:
مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبِ لَمْ يَمْتُ حَ
‘যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে তার গোনাহের জন্য লজ্জা দিল তার দ্বারা সেই গোনাহের কাজ না হওয়া পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না।’ (তিরমিযী)
অতএব এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক হতে হবে।
দোষ অনুসন্ধান ও ছিদ্রান্বেষণ
মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো, ত্রুটির অনুসন্ধান ও ছিদ্রান্বেষণ আর একটি মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের দোষ অনুসন্ধান বা দোষ খুঁজে বেড়ানো নিষিদ্ধ।
ولا تجسسوا .
‘আর দোষ খুঁজে বেড়িও না-গোয়েন্দাগিরি করো না।’ (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১২)
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘দোষ খুঁজে বেড়িও না।
কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ ও গোনাহ খুঁজতে থাকে আল্লাহ তাঁর গোপন দোষ ফাঁস করতে লেগে যান। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করতে লেগে যান তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন সে তার ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকুক না কেন।’ (তিরমিযী)
তুচ্ছ জ্ঞান করা
কোন মুমিনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ। হাদীসে আছে:
بحسب امر ، مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْفَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ.
‘এক ব্যক্তি গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে তার ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।’ (মুসলিম)
আর কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মূলত নিজের মধ্যে অহঙ্কার পোষণ করা:
الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.
‘অহঙ্কার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।’ (মুসলিম)
কাজেই অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মতো অপরাধ থেকে কঠোরভাবে দূরে থাকতে হবে।
উপহাস করা, ঠাট্টা করা
মানুষকে তুচ্ছ মনে করা, নিজেকে বড় মনে করার একটি জঘন্য প্রকাশ হচ্ছে অন্যকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। এ হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ, যা করতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন:
ا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا يسْخَرْ منهم وَلا نِسَاء مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُ
‘হে ঈমানদারগণ! কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। সে হয়ত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে, আর না কোন নারী অপর নারীর উপর প্রতি বিদ্রূপ করবে। হতে পারে সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।’ (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১১)
নিকৃষ্ট অনুমান বা মন্দ ধারণা পোষণ
কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা থেকে অনেক সময় সম্পর্কের ঘাটতি শুরু হয়। পরিণামে তা হয়ত সম্পর্ক বিনষ্ট করে ছাড়ে- এমনকি কখনো শত্রুতায় পরিণত হয়। এজন্য মন্দ পোষণ থেকে বিরত থাকার কথা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ - إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ
‘হে ঈমানদারগণ! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন খারাপ ধারণা অবশ্য গোনাহ।’ (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১২)
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
اياكم وَالظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنِّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.
‘সাবধান! খারাপ ধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা খারাপ ধারণা-অনুমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।’ (বুখারী-মুসলিম)
অপবাদ
কারোর প্রতি সজ্ঞানে মিথ্যা অভিযোগ আনা, দোষ চাপিয়ে দেওয়াকে বলা হয় অপবাদ। এ হচ্ছে মারাত্মক গোনাহ। নিছক মিথ্যা বা নিছক গীবত-চোগলখোরীর চেয়ে এ বড় অপরাধ। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ বলেছেন:
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينًا.
‘যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয় তারা একটি অতি বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট অপরাধের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়।’
(সূরা আহযাব: আয়াত ৫৮)
কাউকে অপবাদ দেয়া থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে হবে।
ক্ষতি সাধন করা
কারো শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বৈষয়িক বা যে কোন ধরনের ক্ষতি সাধন মারাত্মক অপরাধ। অন্যের ক্ষতি সাধনকারীকে হাদীসে অভিশপ্ত বলা হয়েছে:
مَلْعُونَ مَنْ ضَارَ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ.
‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ক্ষতি সাধন করল বা ধোঁকাবাজি করল সে হচ্ছে অভিশপ্ত।’ (তিরমিযী)
مَنْ ضَارَ ضَارَ الله به.
‘যে ব্যক্তি কারো ক্ষতি সাধন করল আল্লাহ তার ক্ষতি সাধন করবেন।’
অতএব কারো যাতে কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না হয়, সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।
ধোঁকা-প্রতারণা
কথাবার্তা, লেনদেনে কাউকে ধোঁকা দেয়া অত্যন্ত অপরাধ। ধোঁকা ও প্রতারণা করা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
ومن غشنا فليس منا .
‘আর যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে সে আমার দলভুক্ত নয়।’ (মুসলিম) কাজেই ধোঁকাবাজ-প্রতারণাকারী প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না।
মনোকষ্ট দেয়া
কোন মুসলমানের পক্ষে তার অপর কোন ভাইয়ের মনে কষ্ট দেয়া অবাঞ্ছিত কাজ। কথা, কাজ, আচরণ বা অন্য কোনভাবেই কোন মুসলমানকে অন্য মুসলমান কষ্ট দিতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
مَنْ أَذَى مُسْلِمًا فَقَدْ أَذَى الله
‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল।’ (তাবরানী)
দান, উপকার ইত্যাদি করে খোঁটা দেয়া
অনেক সময় কাউকে কোন উপকার করে সুযোগ মত খোঁটা দেয়া হয়। খোঁটা দেয়ার কারণে যেমন সম্পর্ক বিনষ্ট হয় তেমনি উপকারের প্রতিফল নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذِى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِنَاءَ النَّاسِ.
‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে ঐ ব্যক্তির মতো নষ্ট করো না যে শুধু লোক দেখাবার জন্যই ধন-মাল ব্যয় করে।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ২৬৪)
খোঁটাবিহীন দানই প্রতিফল পাওয়ার যোগ্য:
الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَا وَلَا أَذًى.
‘যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে এবং খরচ করার পর ইহসান বা উপকারের কথা বলে না কিংবা অনুগৃহীতকে খোঁটা দেয় না তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর কাছে সুরক্ষিত।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ২৬২)
অতএব কাউকে কোন উপকার করে খোঁটা দেয়া অত্যন্ত নীচু মনের পরিচয়। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
হিংসা-বিদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা
হিংসা-বিদ্বেষ মারাত্মক নৈতিক ত্রুটি। এ এক ঘৃণ্য ব্যাধি। তা সমস্ত নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়।
انا ككُم وَالْحَسَدِ فَإِنَّ الْحَسَد يَأْكُلُ الْحَسَنَتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.
‘তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। আগুন যেমন লাকড়ি (জ্বালিয়ে) খেয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি হিংসা নেকী ও পুণ্যকে খেয়ে ফেলে।’ (আবু দাউদ)
কাজেই হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকতে হবে। এ ঘৃণ্য ব্যাধির ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।
সম্পর্ক উন্নয়ন ও মজবুতির উপায়
শুধু সম্পর্ক গড়ে তুললেই হবে না, সম্পর্ক উন্নয়ন ও মজবুতির চেষ্টা চালানো দরকার। পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও মজবুতির জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন
১. মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা,
২. দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ ও সাহায্য-সহযোগিতা,
৩. সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার,
৪. মুলাকাত ও দেখা-সাক্ষাত,
৫. রুগ্ন হলে পরিচর্যা,
৬. মার্জনা,
৭. ব্যক্তিগত ব্যাপারে উৎসুক্য,
৮. সালাম,
৯. মুসাফাহা ও আলিঙ্গন,
১০. হাদিয়া,
১১. শোকরগোজারী বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,
১২. একত্রে আহার বা আপ্যায়ন,
১৩. উৎকৃষ্ট নাম ও পদবী এবং সুন্দরভাবে সম্বোধন,
১৪. আপোস রফা ও অভিযোগ,
১৫. দুআ।
এসব সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো:
মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা রক্ষা
মান-ইজ্জত মানুষের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। মান-ইজ্জত কেউ নষ্ট করলে মানুষ সহ্য করতে পারে না। আবার কেউ যদি কারো মান-ইজ্জত সংরক্ষণ করে তার প্রতি মনের টান ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা যার কাছে পাওয়া যায় না তার সাথে প্রকৃত কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। একজন প্রকৃত বন্ধু সেই হতে পারে যার কাছে তার মান-ইজ্জত-সম্মান নিরাপদ। এ জন্যই কারোর মান-ইজ্জত সংরক্ষণে এগিয়ে আসা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। এ হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায়-কাজ।
হাদীসে আছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘যে মুসলমান তার ভাইয়ের ইজ্জতহানী থেকে কাউকে বিরত রাখতে আল্লাহর প্রতি তার অধিকার এই যে, তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে বিরত রাখবেন।’ (শরহে সুন্নাহ)
দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান
একজন মুমিন তথা দ্বীনি কর্মী তার অপর ভাইয়ের সুখে-দুঃখে অংশ নেবে, তার বিপদাপদে ও অসুবিধায় সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। মুমিনদের সম্পর্কটা হচ্ছে একটি দেহের মত। একের অসুবিধা অন্যে অনুভব করবে।
হাদীসে বলা হয়েছে: ‘তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব,
ভালোবাসা এবং পারস্পরিক দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিতে এমনি দেখতে পাবে যেমন একটি দেহ। যদি তার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয় তো তার সঙ্গে গোটা দেহ জ্বর ও রাত জাগরণের মাধ্যমে তাতে অংশগ্রহণ করে থাকে।’ (বুখারী-মুসলিম)
কাজেই একজন মুমিন আরেক মুমিনের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসাটা স্বাভাবিকভাবেই কাম্য এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ফলে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
وَاللهُ فِي عَوْنِ عَبْدِهِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.
‘আল্লাহ ততক্ষণ তার বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সেই বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।’ (মুসলিম, তিরমিযী)
অতএব পরস্পর সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ ও সাহায্য-সহযোগিতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন উন্নত ও মজবুত হয় তেমনি আল্লাহর সাহায্যও লাভ করা যায়।
সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার
সম্পর্ক উন্নত ও মজবুত করার জন্য সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ। যার ব্যবহার সুন্দর ও কোমল তার সঙ্গে সবারই ভাল সম্পর্ক হয়, আর যার ব্যবহার কর্কশ ও রূঢ় তার সাথে সাধারণত ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। কাজেই দয়া, কোমলতা, সদাচরণ উন্নত সম্পর্কের জন্য অপরিহার্য। মুমিনের পরিচয় দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
المؤمن مالف ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف.
‘মুমিন হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসার মূর্তপ্রতীক। যে ব্যক্তি না ভালোবাসে, না তাকে ভালোবাসা হয় তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।’ (আহমদ, বায়হাকী)
অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:
من اعطى حظه من الرفق اعطى حظه من خير الدنيا والآخرة.
‘যে ব্যক্তিকে নম্র স্বভাব থেকে তার অংশ দেয়া হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকেও তার অংশ দেয়া হয়েছে।’ (শরহে সুন্নাহ)
তাছাড়া মুমিনদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করেছেন:
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.
‘মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করো।’ (সূরা হিজর: আয়াত ৮৮)
হাদীসে হাসি মুখে সাক্ষাত করা, কথা বলাকে অত্যন্ত ফযীলতের কাজ বলা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
والكلمة الطيبة صدقة
‘সুন্দর কথা বলা একটি সদকা বা দান।’ (বুখারী-মুসলিম)
অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে:
اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
‘জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর যদিও তা একটি খেজুরের বিনিময়েও হয়। তাও যদি না পার তাহলে (অন্তত) ভালো বা মধুর কথা দ্বারা যেন সে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করে।’ (বুখারী-মুসলিম)
মোটকথা কোমল ব্যবহার, প্রীতিপূর্ণ আচরণ, সুন্দর ও মধুর কথা উন্নত সম্পর্কের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আল্লাহর কাছেও রয়েছে এর অতীব পুরস্কার।
দেখা-সাক্ষাত
সম্পর্কোন্নয়ন ও মজবুতির জন্য পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতও অতীব ফলপ্রসূ। দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় হয়। এজন্যই দেখা সাক্ষাতের অতীব মর্তবা ও ফযীলত রয়েছে।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখা-সাক্ষাতের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন: ‘তুমি কি জানো, কোন মুসলমান যখন তার ভাইয়েল সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তখন তার পেছনে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকে। তাঁরা তার জন্য দুআ করে।’ (বায়হাকী)
অতএব প্রত্যেক দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীর কর্তব্য তার অপর কর্মী ভাইয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা ও দেখা-সাক্ষাত করা।
রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যা
কোন ভাই রুগ্ন হলে তাকে দেখতে যাওয়া, তার পরিচর্যা করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘যখন কোন মুসলমান তার (রুগ্ন) ভাইয়ের পরিচর্যার জন্য যায় তো ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের মেওয়া বাছাই করতে থাকে।’ (মুসলিম)
অপর হাদীসে আছে:
مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوصُ الرَّحْمَةُ حَتَّى يَجْلِسُ وَإِذَا جَلَسَ اعْتَمَسَ فِيهَا .
‘যে ব্যক্তি রোগীর পরিচর্যা করতে যায় সে রহমতের দরিয়ায় প্রবেশ করে। আর যখন সে রোগীর কাছে বসে, তখন রহমতের মধ্যে ডুবে যায়।’ (মালেক, আহমদ)
মার্জনা
কোন ভাই যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি করে ফেলে তখন অপর ভাইয়ের উচিত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। যারা দুনিয়ার জীবনে অন্যের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন।
وليعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا - أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لكم - والله غفور رحيم
‘তাদের ক্ষমা ও মার্জনার নীতি গ্রহণ করা উচিত। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? বস্তুত আল্লাহ মার্জনাকারী ও দয়া প্রদর্শনকারী।’ (সূরা নূর: আয়াত ২২)
তাই যদি কোন ভাই অন্যায় করে ক্ষমা না করা খুব গোনাহের কাজ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি ভাইয়ের কাছে তার নিজ অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাইলো এবং যে তাকে ক্ষমা মনে করলো না বা তার ক্ষমা কবুল করলো না তার এতখানি গোনাহ হলো যতটা (একজন অবৈধ) শুল্ক আদায়কারীর হয়ে থাকে।’ (বায়হাকী)
অতএব পরস্পর ক্ষমাশীলতা ও মার্জনার নীতি গ্রহণ করা প্রত্যেক মুমিন বিশেষ করে দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদের গ্রহণ করা উচিত।
ব্যক্তিগত ব্যাপারে আগ্রহ
মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত ব্যাপারে আগ্রহ অত্যন্ত কার্যকর। কোন ভাই যদি অপর ভাইয়ের ব্যক্তিগত অবস্থাদির খোঁজ-খবর নেয়, তার সমস্যাদির ব্যাপারে আগ্রহ পোষণ করে, তাহলে পারস্পরিক সম্পর্ক অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া কারও প্রতি আগ্রহ পোষণ, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তার জন্য সক্রিয় হওয়া ঐ ব্যক্তির হকও বটে। হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
ان المسلِمِ لَحْقًّا إِذَا رَاهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ.
‘মুসলমানের হক হচ্ছে এই যে, তার ভাই যখন তাকে দেখবে তখন তার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠবে।’ (বায়হাকী)
অন্য একটি হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে তার কাছ থেকে তার নাম, পিতার নাম, তার গোত্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নিবে। কারণ এর দ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসার শিকড় অধিকতর মজবুত হয়।’ (তিরমিযী)
কাজেই প্রত্যেক কর্মীর উচিত অপর ভাইয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারাদির ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া, তার সমস্যাদি অবগত হওয়া। প্রসঙ্গত জানা দরকার যে, কিছু বিষয় এমন আছে যে ব্যাপারে অন্যদের ঔৎসুক্য কেউ পছন্দ করে না। সে সমস্ত বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এসব থেকে বিরত থাকা চাই।
সালাম
পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য সালাম অত্যন্ত ফলপ্রসূ। সালাম মানুষের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি করে, হৃদ্যতা বাড়ায়, সম্পর্ক গভীর করে, প্রকৃত মুমিন সুলভ গুণ সৃষ্টি করে এবং পরিণামে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করে দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
‘তোমরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর সন্ধান দেব না যা গ্রহণ করে পরস্পরকে ভালোবাসবে? তা হচ্ছে যে তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।’ (মুসলিম)
এজন্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে সালামের প্রসারের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। একে মুসলমানদের পারস্পরিক হকসমূহের অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন। তাই সঠিক অনুভূতি নিয়ে সালামের আদান-প্রদান করলে পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হবে, পরস্পরে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে।
মুসাফাহা ও আলিঙ্গন
সম্পর্ক গভীর করা, পারস্পরিক মনের ক্লেদ দূর করার জন্য মুসাফাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসাফাহা হচ্ছে সালামেরই পূর্ণতা বা সমাপ্তি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
تمام تَحَيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ
‘মুসাফাহা হচ্ছে তোমাদের সালামের বা অভিবাদনের পূর্ণতা প্রাপ্তি।’ (আহমদ, তিরমিযী)
আরেকটি হাদীসে রয়েছে:
تصافحوا يَذْهَبُ الْقِل
‘তোমরা মুসাফাহা করতে থাক, এর দ্বারা শত্রুতা দূর হয়।’
সালাম ও মুসাফাহার মাধ্যমে গোনাহ মাফ হয় ‘আর দুইজন মুসলমান যখন পরস্পর মুসাফাহা করে সমস্ত গোনাহ ঝরে যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।’
পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি ও প্রকাশের আরেকটি মাধ্যম আলিঙ্গন। বিশেষ করে দীর্ঘদিন পর দেখা হলে বা বিশেষ কোন খুশির ব্যাপার ঘটলে আলিঙ্গন করা উত্তম।
হাদিয়া
পরস্পর সম্পর্ক বৃদ্ধি ও আন্তরিকতা সৃষ্টির জন্য হাদিয়া অত্যন্ত ফলপ্রসূ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
تهادُوا تَعْلُوا وَتَذْهَبَ شَحْنَاؤُكُمْ.
‘একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও। এর দ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং হৃদয়ের দূরত্ব ও শূন্যতা দূর হয়ে যাবে।’ (মালেক)
কাজেই সাধ্যমত পরস্পরে হাদিয়া দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। তবে সামাজিক লৌকিকতার চেয়ে আন্তরিকতার প্রকাশটাই প্রয়োজন। ছোট জিনিসই হোক আন্তরিকতার সাথে হাদিয়া বা উপহার দিলে তার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এ হচ্ছে ভালোবাসার প্রকাশ।
শোকরগুজারী বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
কোন ভাইয়ের দ্বারা অপর ভাই উপকৃত হলে অবশ্যই তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অকৃতজ্ঞ প্রকৃতির লোকদের সাথে কারো কোন আন্তরিক সম্পর্ক হতে পারে না।
গুণের মূল্যায়ন ও সম্মান
কারো গুণের ইতিবাচক মূল্যায়ন তার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ। হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার পরিবর্তে যদি কেউ কারো গুণের যথাযথ মূল্যায়ন করে, তার গুণের কদর করে তাহলে তার সঙ্গে অবশ্যই তার হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এজন্য প্রত্যেকের উচিত তার অপর ভাইয়ের মধ্যে যে সমস্ত গুণ ও যোগ্যতা আছে তার সঠিক মূল্যায়ন, এসব গুণ ও যোগ্যতার কদর এবং সম্মান করা।
একত্রে আহার ও আপ্যায়ন
পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য একত্রে খাওয়া-দাওয়া, আদর-আপ্যায়ন করা অত্যন্ত কার্যকর। তাই প্রত্যেকের সাধ্যমত অন্য ভাইদের আদর-আপ্যায়ন করা উচিত।
উৎকৃষ্ট নামে ও পদবীতে সম্বোধন
সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব দৃঢ় করার জন্য একে অন্যকে অবশ্যই সুন্দর-উৎকৃষ্ট নামে ও পদবীতে সম্বোধন করা উচিত। বিকৃত ও অসম্মানজনক নামে সম্বোধন অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। এতে সম্পর্ক খারাপ হতে বাধ্য। একে অন্যকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও স্নেহমাখা সম্বোধন করা উচিত। এতে পরস্পর ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়।
আপোষ করা বা অভিযোগ খণ্ডন
কোন ভাইয়ের সঙ্গে কোন কারণে যদি সম্পর্ক ঘাটতি হয়, কোন বিরোধ বা অভিযোগ দেখা দেয় দ্রুত তার নিরসন করা উচিত। মানুষে মানুষে সম্পর্কজনিত সমস্যা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এ ধরনের অবস্থা চলতে দেয়া উচিত নয়। তাই প্রত্যেকেই নিজের উদ্যোগেই এ সমস্ত সমাধান করতে হবে। কারো সম্পর্কে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হলে তা যথাযথ পন্থায় নিরসনে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। আপোষ মনোভাব ও আন্তরিকতা থাকলে যে কোন সম্পর্কজনিত সমস্যার সমাধানই সম্ভব।
দুআ
পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য, ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য দুআ হচ্ছে অন্যতম মাধ্যম। দুআর মাধ্যমে যেমন পরস্পর আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় তেমনি এ ধরনের দুআ কবুলের খুব সম্ভাবনা। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য দুআ করার সাথে সাথে অন্যদের জন্যও দুআ করতে বলেছেন:
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ.
‘আর তোমাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্যও।’ (সূরা মুহাম্মদ: আয়াত ১৯)
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তার ভাইয়ের অসাক্ষাতে কোন মুসলমান ব্যক্তির দুআ তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য কোন দুআ করে তখনই ঐ নিযুক্ত ফেরেশতা বলে- আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ।’ (মুসলিম)
বস্তুত দুআ করার মাধ্যমে পরস্পরে আন্তরিকতা ও সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং দুআ কবুলের মাধ্যমে প্রভূত কল্যাণ হাসিল হয়।
এহতেসাব বা মুহাসাবা
একটি সংগঠন ও তার কর্মীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য, সংগঠনের মজবুতি ও অগ্রগতির জন্য সংগঠনের ভেতরে পারস্পরিক সমালোচনা ও ভুল ধরিয়ে দেয়া এবং সাংগঠনিক পর্যালোচনার সুযোগ, ব্যবস্থা ও পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। এ ধরনের দরদপূর্ণ, সৎ উদ্দেশ্যে সমালোচনা, ভুল ধরিয়ে দেওয়া ও পর্যালোচনাকে এহতেসাব বলা হয়ে থাকে। এহতেসাবকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।
ক. নিজেই নিজের সমালোচনা বা আত্মসমালোচনা,
খ. কর্মীদের পারস্পরিক সমালোচনা ও
গ. সংগঠনের কোন কাজ, সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি ও সামগ্রিক পরিবেশ ও কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা।
আত্মসমালোচনার বিষয়টি ব্যক্তিগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এখানে তার আলোচনা হচ্ছে না। আমরা সমালোচনা বা এহতেসাবের অপর দুটো ক্ষেত্র নিয়েই আলোচনা করব।
পারস্পরিক সমালোচনা বা এহতেসাব
এক মুমিন আরেক মুমিনের ভাই। একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী অপর কর্মীর ওলী, বন্ধু, অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। তাই একজন মুমিন অপর মুমিনের কল্যাণকামী হবে। একজন দ্বীনের পথের সৈনিক অপর সৈনিকের সার্বিক কল্যাণ কামনা করবে, তাঁর যাবতীয় ক্ষতিকর দিক দূর করার প্রয়াস চালাবে। এই যে কল্যাণ কামনা তা দ্বীনেরই মৌল দাবি। তাই কল্যাণ কামনাকে দ্বীন বলেই হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে:
الدين النصيحة
‘দ্বীন হলো নসিহত।’ (মুসলিম)
আর এ কল্যাণ কামনার দাবি হলো যে, এক মুমিন আরেক মুমিনের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে তা দূর করে দিবে। একজন মুমিন হবে আরেক মুমিনের আয়নাস্বরূপ। একজন মুমিনের মাধ্যমে অপর মুমিন তার ত্রুটিগুলো অবগত হবে। তাই এক মুমিন অপর মুমিনের মন্দ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা করা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে আছে:
ه أذى فليمتُ عنه. إنَّ أَحَدَكُمْ مِرَأَةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ اى .
‘তোমরা প্রত্যেকেই আপন (মুসলমান) ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। সুতরাং যখন তার মধ্যে মন্দ বা ত্রুটি কিছু দেখে তখন সে যেন তা দূর করে দেয়।’ (তিরমিযী)
কাজেই একজন মুমিনের মন্দ বা ত্রুটি দেখলে তা দূর করা তাঁর দায়িত্ব। এহতেসাবের মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা যেতে পারে। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যেহেতু একজন মুমিন অন্য মুমিনের জন্য আয়না, একজন আরেক জনের ভাই, তাই একজনের ক্ষতির বিষয় থেকে অন্যজন তাকে রক্ষা করা কর্তব্য।
وب المزمن مرأة المؤمن والمؤمن أخو الْمُؤْمِنِ يَكُفَّ شِيعَتِهِ وَيَحوطه من ورانه.
‘এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না। একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের ভাই। সে তাকে ক্ষতিকর ও ধধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার স্বার্থ রক্ষা করে।’ (তিরমিযী, আবু দাউদ)
বস্তুত ত্রুটি-বিচ্যুতি যা একজন মুমিনের জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক তা দূর করাও অন্য মুমিনের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব এহতেসাবের মাধ্যমে পালন করা যেতে পারে। বিশেষ করে সংগঠনের কর্মীদের পারস্পরিক সংশোধন ও ত্রুটি দূর করার জন্য এহতেসাব অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ।
এহতেসাবের পদ্ধতি
পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করার জন্য এহতেসাব বা পারস্পরিক সমালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে যথানিয়মে ও সঠিক পন্থায় তা করা না হলে অনেক সময়ই ক্ষতিকর ও মারাত্মক হতে পারে। ভুল পন্থায় এহতেসাব করতে গিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপও হয়ে যেতে পারে। তাই সঠিক পন্থায় এহতেসাব করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।
১. প্রথমত কারো আচার-আচরণে, কাজে-কর্মে কোন ত্রুটি দেখলে বা মনের মধ্যে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হলে মনের মধ্যে তা পুষে না রেখে সময়-সুযোগ করে সংশ্লিষ্ট ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে অত্যন্ত দরদের সাথে তার সামনে পেশ করা প্রয়োজন। বিষয়টি যদি তিনি মেনে নেন তাহলে এহতেসাবের প্রক্রিয়া এখানেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।
২. যদি সংশ্লিষ্ট ভাই অভিযোগ মানতে না চান বা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে খুব ক্ষতিকর কিছু না হলে এ নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। মানাবার জন্যে জিদ ধরাও ঠিক নয়।
৩. দৃষ্টি আকর্ষণ ও মেনে নেয়ার পরও যদি বার বার ঐ ভাইয়ের মধ্যে একই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে বিষয়টি সংগঠন ও আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলে তা সংগঠনের দায়িত্বশীলগণের গোচরে আনা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে তাঁর অনুমতিক্রমে এহতেসাব বৈঠকেও উঠানো যেতে পারে।
৪. এহতেসাব বা সমালোচনা যেখানে সেখানে করা যাবে না। নির্দিষ্ট বৈঠকে অথবা কোন বৈঠকে গৃহীত এজেণ্ডাক্রমেই তা করা যাবে।
৫. সমালোচনাকারী ব্যক্তি আল্লাহকে হাজির নাজির মেনে, নিজের মনের অবস্থা যাচাই করে দেখবেন যে, তিনি সদুদ্দেশ্যে ও শুভাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই সমালোচনা করেছেন, না ব্যক্তিগত কোন কারণে সমালোচনা করেছেন। যদি উদ্দেশ্য সত্য হয় তাহলে এহতেসাব করা যেতে পারে। অন্যথায় অন্যের এহতেসাবের চেয়ে নিজের আত্মসমালোচনা ও সংশোধন প্রয়োজন।
৬. সমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করতে পারবেন যে, সমালোচনাকারী সত্যি সত্যিই আন্তরিকভাবে সংশোধন কামনা করেছেন।
৭. সমালোচনাকারী বাস্তব প্রমাণ ছাড়া শুধু অনুমান বা সন্দেহের ভিত্তিতে কোন কথা পেশ করবে না। অনুমান ও সন্দেহ গোনাহের নামান্তর।
৮. সমালোচনাকারী কোন কথা মানাবার জন্য জিদ ধরবেন না বা কথা কাটাকাটি করবেন না।
৯. সমালোচনার ধারা অব্যাহত চলতে থাকা উচিত নয়।
সমালোচনাকারীকে আরো কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে:
১. দোষ অনুসন্ধান, ছিদ্রান্বেষণ করে দোষ বের করা যাবে না। এ সবই হারাম।
২. দোষ ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পেশ করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে নির্দিষ্ট এহতেসাব বৈঠকে পেশ করতে হবে। কিন্তু এর বাইরে অন্যদের নিকট বলা বা প্রকাশ করা গীবত। গীবত ইসলামে হারাম এবং মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত ঘৃণ্য।
৩. সন্দেহের ভিত্তিতে কারো সম্পর্কে কোন কথা বলা যাবে না; সন্দেহ গোনাহ।
৪. অপবাদ বা মিথ্যা দোষারোপ করা যাবে না। শরীয়তে অপবাদ বা তোহমতের কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।
৫. ব্যক্তিগত দোষ যা প্রকাশ হয়ে পড়লে ব্যক্তির মান-সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা ব্যক্তি নিজেও তা গোপন রাখতে চায় অথচ তা সাংবিধানিক বা আন্দোলনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত বা অন্যের সংক্রান্ত কিছুই নয় এমন ত্রুটি গোপন রাখাই শরীয়তের বিধান। হাদীসে আছে:
من راى عورة فسترها كان كمن احيى مؤدة
‘যে ব্যক্তি কারো কোন দোষ দেখে গোপন রাখল সে ঐ ব্যক্তির মতো যে জীবন্ত প্রোথিত কোন মেয়েকে বাঁচাল।’ (আহমদ ও তিরমিযী)
যার এহতেসাব করা হবে তার করণীয়
১. যে ব্যক্তির সমালোচনা বা এহতেসাব করা হবে তাকে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সমালোচকের বক্তব্য শোনা ও সেগুলো ভেবে দেখা কর্তব্য। অভিযোগ সত্য হলে অকপটে স্বীকার করা উচিত এবং সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। অভিযোগ অথবা অভিযোগের কোন অংশ সত্য না হলে তা যুক্তি-প্রমাণ দিয়েই খণ্ডন করা উচিত। সমালোচনা শুনে রাগ করা, ক্ষেপে যাওয়া, উত্তেজিত হওয়া অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার লক্ষণ।
২. সমালোচনাকারীর প্রতি মনে মনে কোন ক্ষোভ রাখা মোটেই সঙ্গত নয়; বরং তিনি ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন বলে সমালোচিত ব্যক্তির কর্তব্য সমালোচনাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
৩. কেউ (অন্যায়) সমালোচনা করলেও ক্ষিপ্ত না হয়ে শান্তভাবে অভিযোগ খণ্ডন করে সমালোচনাকারীর ভুল বা ত্রুটি তুলে ধরা উচিত। সমালোচনাকারীর প্রতি অভিযোগ না রেখে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।
বস্তুত একমাত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে একান্ত আন্তরিকতার সাথে সঠিক পন্থায় এহতেসাব করলেই তা ফলপ্রসূ হবে এবং এ ধরনের এহতেসাবই প্রয়োজন ও কল্যাণকর। সংগঠনের পরিমণ্ডলে এরূপ এহতেসাব চালু থাকা আবশ্যক।
সাংগঠনিক এহতেসাব বা মুহাসাবা
ব্যক্তিবর্গ বা কর্মীদের মধ্যে যেমন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে তেমনি সংগঠনের ভেতরে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করতে পারে। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা যদি চিহ্নিত না করা হয়, এসব ব্যাপারে যদি দৃষ্টি আকর্ষণ না করা হয়, এগুলো দূর করার জন্য যদি কোন পদক্ষেপ না নেয়া হয় তাহলে ক্রমে ক্রমে ত্রুটি আরো বৃদ্ধি পাবে, দুর্বলতা আরো বড় হবে। তাই সংগঠনের বা দলের সংস্কার, সংশোধন এবং সুস্থতা-গতিশীলতা ও অগ্রগতির জন্য সাংগঠনিক পর্যায়েও মুহাসাবা বা সমালোচনা ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সাংগঠনিক মুহাসাবার ব্যবস্থা না থাকলে হয়ত অগোচরেই নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, কর্মীদের মধ্যে অন্ধত্ব ও গোঁড়ামি, কার্যক্রমে বিকৃতি, নেতৃত্বের স্বেচ্ছাচারিতা, ভুলকে শুদ্ধ বলে চালিয়ে দেয়ার মানসিকতা, ভুল স্বীকার না করার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। মুহাসাবার সুযোগ না থাকলে কর্মীদের ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে পারে। মুহাসাবার মাধ্যমে এসব প্রতিকার করা সম্ভব। মুহাসাবা ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মীরা সচেতন হয়, নেতৃবৃন্দ সতর্ক ও হুঁশিয়ার হন। তাই সঠিক এহতেসাব বা মুহাসাবা সংগঠনের প্রাণস্বরূপ।
সাংগঠনিক মুহাসাবা বাা সমালোচনা অত্যাবশ্যক কিন্তু যত্রতত্র ও অনিয়মে সমালোচনা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই সঠিক বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সাংগঠনিক মুহাসাবা বা সমালোচনা হতে হবে।
সাংগঠনিক মুহাসাবা মূলত পর্যালোচনা ও মূল্যায়নধর্মী। তাই এ ধরনের মুহাসাবাকে পর্যালোচনা নামেই আখ্যায়িত করা হয়।
সাংগঠনিক পর্যালোচনা দুই ভাগে হতে পারে। একটি ব্যক্তিগতভাবে, অপরটি বৈঠকী পর্যায়ে।
ব্যক্তিগত পর্যালোচনা
ব্যক্তিগতভাবে একজন কর্মী সংগঠনের কোন বিষয়ের পর্যালোচনা করতে পারেন, কোন কিছু ত্রুটিপূর্ণ মনে করলে তা তুলে ধরতে পারেন, বলতে পারেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। তবে তা সবই হতে হবে যথানিয়মে ও যথাস্থানে। দায়িত্বশীল বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট বা সংগঠনের বৈধ কোন ফোরাম বা শূরায় পেশ করা যাবে। কর্মীদের নিজেদের মধ্যে তা চর্চা, লাগামহীন সমালোচনা, অসন্তোষ প্রকাশ ও তা ছড়ানো মোটেই কল্যাণকর নয়, নয় সঙ্গত। এতে ক্ষতি ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। সংগঠনের কল্যাণ চাইলে কর্মীরা যা অনুভব করবেন তা যথানিয়মে সংগঠনকে অবহিত করাই কর্তব্য, তুলে ধরাই দায়িত্ব। তা না করে নিজেদের মধ্যে চর্চা, সংগঠন সম্পর্কে অসন্তোষ ও ভুল ধারণা সৃষ্টি কোন পর্যালোচনা বা এহতেসাব নয়। এ হচ্ছে সংগঠন-আন্দোলনের ক্ষতি করার প্রয়াস। তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
বৈঠকী পর্যালোচনা
সংগঠনের প্রতিটি বিষয়েই প্রয়োজন মত নিয়ম মাফিক বৈঠকী আলোচনা হতে পারে, পর্যালোচনা হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কেন্দ্রীয় বিষয় কেন্দ্রীয় পরিষদেই আলোচনা হবে। শাখার বিষয় শাখায়ই পর্যালোচনা হবে। অবশ্য শাখার বিষয়টি কেন্দ্রেও পর্যালোচনা হতে পারে। শাখা কেন্দ্রের কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচির পর্যালোচনার অধিকারী নয় তবে কেন্দ্রের কোন সিদ্ধান্ত বা অন্য বিষয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হলে তা কেন্দ্রে জানানো ও ব্যাখ্যার আবেদন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পরিষদকে আলোচনা করতে দাবিও জানানো যেতে পারে। কিন্তু গঠনতন্ত্রের বা বিধিবদ্ধ নিয়মের বাইরে কোন সমালোচনা, পর্যালোচনাই কল্যাণকর নয়।
বৈঠকী পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তি বৈঠকে খোলাখুলি বক্তব্য রাখার অধিকারী। তবে সিদ্ধান্ত হবে সর্বসম্মত বা অধিকাংশের মত অনুযায়ী। ব্যক্তিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ও পর্যালোচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এক্ষেত্রে জিদ ধরা, হঠকারিতা বা গোঁড়ামি করা মোটেও ঠিক নয়। আবার বৈঠকের পর্যালোচনা বৈঠকের বাইরে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলে প্রয়োজনে যথার্থ ফোরামে ওঠানো যেতে পারে, কিন্তু বিধি-বহির্ভূতভাবে চাপ সৃষ্টি, অসন্তোষ প্রকাশ কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। এতে শুধু অকল্যাণই হবে।
বস্তুত সাংগঠনিক পর্যালোচনা বা মুহাসাবার মাধ্যমে সংগঠনের প্রভৃত কল্যাণ হতে পারে, সংগঠনের সংশোধন হতে পারে, সংগঠন সঠিক পথে চলতে পারে। তবে বিধি-বহির্ভূত ও অনিয়মে পর্যালোচনা সংগঠনের ক্ষতিও ডেকে আনতে পারে। তাই যথার্থ সাংগঠনিক পর্যালোচনা বা মুহাসাবার পর্যাপ্ত সুযোগ সংগঠনের ভেতরে থাকা চাই।
অর্থব্যবস্থা বা বায়তুল মাল
ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই দ্বীনি সংগঠনের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে তহবিল গঠন। এই তহবিলকে সাধারণত ‘বায়তুল মাল’ নামে আখ্যায়িত করা হয়। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগারই প্রকৃত বায়তুল মাল, তবে দ্বীনি সংগঠন যেহেতু দ্বীনি রাষ্ট্র ও ব্যবস্থা কায়েমের জন্যই কর্মরত তাই তার তহবিলকেও বায়তুল মাল বলা হয়ে থাকে।
দ্বীনি আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দান করা, অর্থ ব্যয় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন:
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ.
‘আল্লাহর পথে খরচ কর।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ৯৫)
প্রকৃত কল্যাণ ও পুণ্য লাভ করার জন্য প্রিয় বস্তু আল্লাহ তাআরার পথে ব্যয় করা অপরিহার্য:
لَن تَنَالُ اللَّهَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.
‘তোমাদের প্রিয় ও ভালোবাসার বস্তু (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই পুণ্য লাভ করতে পারবে না।’ (সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ৯২)
তাই আল্লাহর নির্দেশ উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ من الأرض.
‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ এবং আমি যা কিছু তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট ও পবিত্র অংশ ব্যয় কর।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ২৬৭)
কাজেই আল্লাহর পথে মুমিনদের ঠিকমত ব্যয় করতে হবে। বিশেষ করে জিহাদের জন্য, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দ্বীন সংরক্ষণের আন্দোলনের জন্য খরচ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনুল কারীমে জিহাদ করার নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই মাল ও জান উভয়টি দিয়ে জিহাদের কথা বলা হয়েছে:
تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
‘তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর মাল ও জান দিয়ে।’ (সূরা সফ: আয়াত ১১)
অতএব যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কাজে, আন্দোলনের কাজে রত তাদের প্রথমেই সাধ্যমত মালের জিহাদ করতে হবে। জিহাদের কাজে, দ্বীনি আন্দোলনের কাজে অর্থ ব্যয় করা অতীব সওয়াবের কাজ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
مَنْ انْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمَانَةِ ضعف.
‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) খরচ করলো তার জন্য তার সাতশ গুণ লেখা হয়।’ (তিরমিযী)
আরো একটি হাদীসে আছে:
مَنْ أَرْسَلَ نَفَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ ذِرْهُم سَعِيانَةِ الله وَانْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ فَلَةٌ بِكُلِّ ذِرْهُم درَاهِم وَمَنْ عَرَ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ الله وَ سبعمائة الف دراهم.
‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) খরচের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠালো কিন্তু নিজে বাড়িতে রয়ে গেল (তার প্রেরিত) প্রতি দিরহামের বিনিময়ে সাতশ দিরহামের সওয়াব পাবে। আর যে নিজে স্বয়ং জিহাদে অংশ নিল এবং মালও ব্যয় করলো সে ব্যক্তি প্রত্যেক দিরহামের জন্য সাত লক্ষ দিরহামের সওয়াব পাবে।’ (ইবনে মাজাহ)
কাজেই আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করা অতীব সওয়াবের কাজ। তাই প্রত্যেক কর্মীকে সাধ্যমত নিয়মিতভাবে আন্দোলন ও সংগঠনের তহবিলে জিহাদের নিয়তে, তার প্রস্তুতির নিয়তে অর্থ ব্যয় করতে হবে।
বস্তুত সংগঠনের বায়তুল মালের মূল উৎসই হচ্ছে কর্মীদের মাসিক আর্থিক সাহায্য। সাথে সাথে শুভাকাঙ্ক্ষীদের দানও গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রত্যেক কর্মীকে আন্দোলন ও সংগঠনের বায়তুল মাল মজবুত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এটিও সংগঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কর্মীরা নিজেরা সাধ্যমত আর্থিক কুরবানী তো করবেই তৎসঙ্গে আন্দোলন-সংগঠনের শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী ও জনগণের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বায়তুল মালকে শক্তিশালী করা এবং আন্দোলনের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
অন্য দিকে বায়তুল মালের অর্থকে আমানত মনে করে মিতব্যয়িতার সাথে খরচ করতে হবে। তার যথাযথ হিসাবও সংরক্ষণ করতে হবে। বায়তুল মাল সংগ্রহ ও ব্যয় করা নিয়ে যাতে কোন সমস্যা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
সাংগঠনিক পরিবেশ
একটি ইসলামী সংগঠনের জন্য তার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক পরিবেশ যদি কাম্য মানের না হয়, পরিবেশ যদি সুন্দর না হয়, তাহলে সংগঠনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। নানা সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। ত্যাগী ও আন্তরিক কর্মী বাহিনী তৈরিতে বাঁধার সৃষ্টি হয়। মোটকথা সংগঠনের অগ্রগতি ও মজবুতির জন্য উন্নত সাংগঠনিক পরিবেশ অতীব জরুরি।
সাংগঠনিক কাম্য পরিবেশ কাকে বলে
একটি আন্দোলন ও সংগঠনের কাম্য পরিবেশ হচ্ছে সেই পরিবেশ যা হবে:
১. আন্দোলনের লক্ষ্যে তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে এগুবার অনুকূল। যে পরিবেশ সংগঠনের লক্ষ্যপাণে এগোনোর পথে বাধ্যতা অবশ্যই প্রতিকূল পরিবেশ।
২. ঈমান ও আমলের বিকাশের অনুকূল অর্থাৎ সংগঠনের পরিবেশ এমন হওয়া চাই যাতে করে জনশক্তির ঈমানের মজবুতি অর্জন ও আমল-আখলাক উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরি হয়। যে সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে কর্মীদের চরিত্র ও আমল সংশোধিত হয় না, কর্মীরা আত্মগঠনে উদ্বুদ্ধ হয় না তা অবশ্যই অবাঞ্ছিত পরিবেশ। কাম্য পরিবেশের দাবিই হচ্ছে যে, কর্মীবাহিনী ও জনশক্তি দিন দিন আত্মগঠন ও চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে উৎসাহিত হবে, তাদের মান বৃদ্ধি পাবে।
৩. ক্রমবর্ধমান সার্বিক উন্নয়নের, তরবিয়তের বা প্রশিক্ষণের অনুকূল। কর্মীদের জ্ঞানার্জন, দক্ষতা বৃদ্ধি সহ যাবতীয় দিকের উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ থাকা চাই। যে সংগঠনের পরিবেশ কর্মীদের সার্বিক উন্নয়নের অনুকূল নয়, তা অবশ্যই যথার্থ পরিবেশ নয়।
৪. মানবিক গুণ ও যোগ্যতার বিকাশের অনুকূল সংগঠনের পরিবেশ এমন হতে হবে যাতে জনশক্তি বা কর্মী বাহিনীর বিভিন্নমুখী মানবিক গুণাবলীর বিকাশ হয়, বিভিন্ন প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ হয়। সংগঠনের পরিবেশ যদি কর্মীদের প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। আন্দোলন সফল করতে যেহেতু বহুমুখী লোকজনের প্রয়োজন, বিভিন্নমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী ও নেতৃত্বের প্রয়োজন তাই লোকদের যোগ্যতা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।
৫. ত্যাগ ও কুরবানীর ভাবধারা সৃষ্টির অনুকূল। দ্বীনি আন্দোলন সফলতার জন্য ত্যাগ ও কুরবানী অত্যাবশ্যক। অপরিসীম ত্যাগ-কুরবানী ছাড়া কোন আন্দোলন এগোতে পারে না। সফলতা লাভ করতে পারে না। তাই সংগঠনকে অবশ্যই কর্মীদের মধ্যে ত্যাগ-কুরবানীর ভাবধারা সৃষ্টির প্রয়াস চালাতে হবে। আর সেই ভাবধারা সৃষ্টির জন্য সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ তার অনুকূল হওয়া চাই। যে সাংগঠনিক পরিবেশে কর্মীদের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হয়, কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ হয় তাই কাম্য পরিবেশ। আর যে পরিবেশ কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ত্যাগ-কুরবানীর ব্যাপারে অনীহার জন্ম দেয় তা অবশ্যই অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর পরিবেশ। কাজেই কাম্য পরিবেশ মানেই ত্যাগ ও কুরবানীর ভাবধারা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ।
কাম্য সাংগঠনিক পরিবেশ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল
সাংগঠনিক কাম্য পরিবেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সেগুলো প্রধানত নিম্নরূপ:
১. সঠিক পরিচালনা ও নির্দেশনা: সাংগঠনিক পরিচালনা যদি যথার্থ হয় তাহলে কাম্য মানের পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সংগঠনের পরিবেশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নষ্ট হয় নেতৃত্ব দান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণে। পরিচালনা যথার্থ না হলে কাম্য পরিবেশ সৃষ্টি খুবই কঠিন। যেহেতু পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রধানত নেতৃত্বের, এক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে অবশ্যই পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাই ভাল ও কাম্য পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে নেতৃত্ব ও পরিচালনা সঠিক ও যথার্থ হওয়া চাই।
২. যথার্থ আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা: আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর কাম্য পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল। যেখানে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তের আনুগত্যের ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে, যেখানে কর্মীবাহিনী নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিকভাবে মেনে চলে না সেখানে ভাল কোন পরিবেশ থাকার কথা নয়। সঠিক আনুগত্য থাকলে, নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে সবাই কঠোর ও যত্নবান হলে অবশ্যই ভাল পরিবেশ গড়ে উঠবে।
৩. ‘শূরা’ বা পরামর্শ ব্যবস্থা: দ্বীনি আন্দোলনে শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ভাল পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে শূরায়ী পদ্ধতির অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। যেখানে পরামর্শ করে কাজ চলে না, স্বেচ্ছাচারিতা চলে সেখানে কোন সাংগঠনিক কাম্য পরিবেশ আশা করা যায় না। যেখানে কর্মীদের বা সংশ্লিষ্ট লোকদের মতামত শোনা হয় না, তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় না, যেখানে ব্যক্তি বা কোন গ্রুপের মতামত শোনা হয় না, তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় না, যেখানে ব্যক্তি কোন গ্রুপের মতামত ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থাকে সেখানে পরিবেশ বিষাক্ত ও বিক্ষুব্ধ হতে বাধ্য। তাই কাম্য পরিবেশ চাইলে পরামর্শ বা শূরায়ী ব্যবস্থার যথার্থ অনুশীলন প্রয়োজন।
৪. যাবতীয় বিষয় নিয়মানুগ পন্থায় সম্পাদন: পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য যাবতীয় বিষয়াদি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নির্দেশ প্রদান, কর্মসূচি গ্রহণ, কর্মবণ্টন, বাস্তবায়ন, রিপোর্ট গ্রহণ ও তৈরি, পর্যালোচনা, সমালোচনা, এহতেসাব, কর্মীদের সংশোধন সবকিছুই নিয়মানুগ পন্থায় হতে হবে। অনিয়মে কাজ করলে যতই আন্তরিক থাকুক, উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক সাংগঠনিক পরিবেশ নষ্ট হতে বাধ্য। উদ্দেশ্য ও নিয়ত ভাল থাকলেই ভাল কাজ হয় না। পদ্ধতি ও তরিকাও উত্তম এবং যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। ভুল পদ্ধতিতে বা নিয়ম বহির্ভূত পন্থায় কাজ করলে বা করতে চাইলে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া কোন পথ থাকে না। তাই কাম্য পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে নিয়মানুগ পদ্ধতিতেই সব কাজ সম্পাদন প্রয়োজন। কোন অবস্থায়ই নিয়ম-বহির্ভূতভাবে কাজ করা প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। নিয়মের উপর সবাইকে দৃঢ় হতে হবে, কঠোর হতে হবে। তাহলে কাম্য পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।
৫. সংগঠনের গঠনতন্ত্র যথার্থভাবে অনুসরণ: গঠনতন্ত্র হচ্ছে একটি সংগঠনের গঠন প্রণালী, পরিচালনা ও কর্মসূচির মৌলিক দলিল। সংগঠনের মৌলিক নিয়ম-কানুন গঠনতন্ত্রে সংবিধিবদ্ধ থাকে। তাই সংগঠনকে যথার্থভাবে পরিচালনা করতে চাইলে, নিয়ম মাফিক সবকিছু করতে চাইলে অবশ্যই গঠনতন্ত্রের যথার্থ অনুসরণ করতে হবে। গঠনতন্ত্রের অনুশীলন যথার্থভাবে না হলে অনিয়ম, খামখেয়ালী, স্বেচ্ছাচারিতা, শৃঙ্খলাহীনতা, একের কাজে অন্যের হস্তক্ষেপ, অপপ্রয়োগ ইত্যাদি বহু সমস্যা দেখা দিতে পারে। ফলে সংগঠনের পরিবেশ বিনষ্ট হতে বাধ্য। অতএব সাংগঠনিক পরিবেশের জন্য গঠনতন্ত্রের যথাযথ অনুশীলন ও অনুসরণ অত্যাবশ্যক।
৬. ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা: দ্বীনি সংগঠনের কাম্য পরিবেশ শুধু কতগুলো নিয়ম-নীতির উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং কর্মীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একে অন্যের সহযোগিতার মনোভাবের উপরও নির্ভরশীল। ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ না থাকলে, একে অন্যের সহযোগিতা না থাকলে ভাল পরিবেশ হতেই পারে না। দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত হওয়া চাই। একে অন্যের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী হওয়া চাই। ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক যত দৃঢ় হবে পরিবেশ ততই সুন্দর ও উন্নত হবে। সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব অতীব প্রয়োজন। তাই এসব বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে।
৭. ইনসাফ ও সাম্য: যথার্থ পরিবেশের জন্য সংগঠনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইনসাফ, কর্মবণ্টনে ইনসাফ, আচরণের ক্ষেত্রে ইনসাফ ছাড়া ভাল কোন পরিবেশই গড়ে উঠবে না। দ্বীনি সংগঠনে যদি ইনসাফ না থাকে, সাম্যের অভাব ঘটে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় তাহলে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সংগঠনের ভেতরে যত সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেয়, গ্রুপিং-পাল্টা গ্রুপিং সৃষ্টি হয়, নানা কোন্দল দানা বেঁধে ওঠে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ইনসাফের অভাব ও সাম্যের ঘাটতি। তাই উন্নত পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে ইনসাফ সংরক্ষণ ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় নজর দিতে হবে।
৮. সর্বক্ষেত্রে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন: দ্বীনি সংগঠন ও আন্দোলন দ্বীনের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়। তাই দ্বীনি আন্দোলনের প্রতিটি কাজে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল ও আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার মনোভাবকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যদি দ্বীনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী বাহিনী সব কাজে তাকওয়া বা খোদাভীতির নীতি গ্রহণ না করেন, তাহলে দ্বীনি আন্দোলন ও সংগঠন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না, পরিবেশ সুন্দর হতে পারে না। তাই পরিবেশকে সুন্দর ও সুষ্ঠু করতে হলে সর্বক্ষেত্রে তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘আমি নসিহত করছি তুমি তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর। এটা তোমার সমস্ত কাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেবে।’ (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান)
অতএব দ্বীনি সংগঠনে সুন্দর কাম্য পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সর্বক্ষেত্রে তাকওয়ার নীতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর করা সম্ভব নয়।
পরিবেশ ক্ষুণ্ণকারী বিষয়সমূহ
এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা সাংগঠনিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ করে, ক্ষেত্র বিশেষ পরিবেশকে বিনষ্ট করে দেয়। সেগুলো প্রধানত নিম্নরূপ:
১. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ: সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি অধিক মাত্রায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধ দ্বারা আক্রান্ত হয়, আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা দেয় তখন সামষ্টিক চরিত্র ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। ফলে সাংগঠনিক পরিবেশ নষ্ট হয়। সংগঠনের ভেতরে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।
২. ব্যক্তিগত ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ: প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি ব্যক্তিগত জীবন আছে। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপারে অহেতুক, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কেউ হস্তক্ষেপ করুক, নাক গলাক কোন ব্যক্তি তা পছন্দ করে না। এখন যদি বড় ধরনের সাংগঠনিক প্রয়োজন ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু হয় তাহলে পরিবেশ বিনষ্ট হতে বাধ্য। এমনকি বড় ধরনের সাংগঠনিক প্রয়োজনেও কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হলে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিজ্ঞতার সাথে এগোতে হবে। অন্যথায় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
৩. মেযাজের ভারসাম্যহীনতা: দায়িত্বশীল ও কর্মীদের মেযাজের ভারসাম্য-হীনতাই সাংগঠনিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তাই মেযাজের ভারসাম্য রক্ষা সংগঠনের পরিবেশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।
৪. নিজের চিন্তাকে চূড়ান্ত মনে করা: অনেক দায়িত্বশীল নিজের চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। নিজের চিন্তাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন। অন্যের চিন্তাকে মোটেই গুরুত্ব দিতে চান না। অন্যের চিন্তা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। এ ধরনের মন-মানসিকতা ও প্রবণতা থাকলে সাংগঠনিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাই সামষ্টিক চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, অন্যের চিন্তার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
৫ . অসহনশীলতা: সাংগঠনিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার জন্য অসহনশীলতা ও ধৈর্যের অভাব যথেষ্ট দায়ী। একটি সংগঠন ও আন্দোলনে অপছন্দনীয়, অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে সহনশীলতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন। এর পরিবর্তে যদি অসহনশীলতা ও অধৈর্য দেখা দেয়, তাহলে সাংগঠনিক পরিবেশ রক্ষা করা কঠিন। তাই পরিবেশ রক্ষা করতে হলে সহনশীলতা ও ধৈর্যশীলতা প্রয়োজন।
৬. কথাবার্তায়, আচরণে, মন্তব্য, আবেগ ইত্যাদি প্রকাশে নিয়ম রক্ষা না করা: পরিবেশের জন্য নিয়ম রক্ষা করা অতীব জরুরি। কেউ যদি নিয়ম বহির্ভূতভাবে কথাবার্তা বলে, মন্তব্য করে বসে, আবেগ প্রকাশ করে বা আচার-আচরণ করে তাহলে পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।
৭. পরিবেশের দিকে লক্ষ্য না রাখা: এমন অনেকে আছেন যারা কথাবার্তা বলার সময়, মন্তব্য করার সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে খেয়াল রাখেন না। যাদের সামনে কথা বলছেন, মন্তব্য করছেন, শ্রোতাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া তা বিবেচনা করেন না। এসব ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। সব সময় পরিবেশের দিকে খেয়াল রেখে কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও মন্তব্য করা উচিত। এক্ষেত্রে অসতর্কতা অত্যন্ত ক্ষতিকর।
৮. প্রান্তিকতা ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি: সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে একপেশে মনোভাব, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, প্রান্তিকতা ও চরমপন্থী প্রবণতা, একগুঁয়েমি বা কোন বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই পরিবেশ রক্ষা করতে হলে এসব প্রবণতা অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে।
৯. অতি কঠোরতা বা অতি শিথিলতা: সংগঠনের জন্য সব ব্যাপারেই মধ্যমপন্থা প্রয়োজন। আপোষহীনতার নামে অতি কঠোরতাও ক্ষতিকর আবার উদারতার নামে অতি শিথিলতাও ক্ষতিকর। সংগঠনের পরিবেশ রক্ষা করতে হলে যুক্তিহীন কঠোর মনোভাব ও শিথিল মনোভাব উভয়ই পরিত্যাজ্য। মাঝামাঝি মধ্যমপন্থী ভারসাম্যের মনোভাবই উত্তম। অবশ্য প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে আবার প্রয়োজনে উদারও হতে হবে। এক্ষেত্রে মাত্রাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
১০ . গীবত, তোহমত, ছিদ্রান্বেষণ, চোগলখোরী: পরিবেশের জন্য এসব অত্যন্ত মারাত্মক। এ সমস্ত গর্হিত ও হারাম কাজ সম্পূর্ণ পরিহার করতে না পারলে কাম্য পরিবেশ গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয়। তাই সাংগঠনিক ভাল পরিবেশ চাইলে এ সমস্ত মারাত্মক ত্রুটিগুলো অবশ্যই দূর করতে হবে। সংগঠনের পরিবেশে এসবের চর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে প্রয়োজনে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে।
১১ . যথার্থ এহতেসাবের অভাব: সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট লোকদের দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য এহতেসাবের যথার্থ পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। যেখানে এহতেসাবের পরিবেশ থাকে না বা এহতেসাবের দ্বার রুদ্ধ করে রাখা হয় সেখানে কাম্য সাংগঠনিক পরিবেশ বিরাজ করতে পারে না। আবার অনিয়মে এহতেসাব, এহতেসাব নামে দোষচর্চা ও পরিবেশকে নষ্ট করে তাই যথার্থ এহতেসাবের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাতে পরিবেশ সুন্দর হবে, সুস্থ থাকবে।
১২. অবিশ্বাস ও সন্দেহ: সংগঠনের ভেতরে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ, আস্থাহীনতা পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে মতপার্থক্যের কারণে যদি কারো প্রতি সন্দেহ করা হয়, তাহলে পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক। কাজেই সংগঠনের পরিমণ্ডল থেকে পারস্পরিক অনাস্থা ও সন্দেহ দূর করতে হবে। আস্থা, বিশ্বাস ও পরস্পর সুধারণা বজায় রাখতে হবে।
১৩. গ্রুপিং ও উপদলীয় কোন্দল: সংগঠনের পরিবেশের জন্য গ্রুপিং, উপদলীয় কোন্দল, বিভিন্নমুখী লবিং ও তাদের তৎপরতা অত্যন্ত মারাত্মক। গ্রুপি-লবিং-এর পরিণতি সংগঠনে ভাঙ্গন পর্যন্ত ধরাতে পারে। তাই সংগঠনে কোন অবস্থায় গ্রুপিং বা উপদল সৃষ্টি করতে দেওয়া যাবে না। কঠোরভাবে এসব পরিহার করতে হবে, বন্ধ করতে হবে। একবার সংগঠনে গ্রুপিং জন্ম হলে আর কাম্য পরিবেশ আশা করা যায় না। তাই এসব ব্যাপারে সতর্ক হওয়া সবার দায়িত্ব।
১৪ . পক্ষপাতিত্ব ও বেইনসাফী: সংগঠনের ভেতরে যদি পক্ষপাতিত্ব থাকে, কারো ব্যাপারে বেইনসাফী করা হয়, তাহলে পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। এজন্য পরিবেশ রক্ষা করতে হলে পক্ষপাতিত্ব বা বেইনসাফী পরিহার করে চলতে হবে।
১৫. চিন্তার অবদমন: সংগঠনের ভেতরে যদি সৃজনশীল চিন্তাকে অবদমন করা ও মতামত দাবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হবেই। এর প্রতিক্রিয়াও হয় মারাত্মক। তাই পরিবেশ বজায় রাখতে হলে চিন্তার অবদমন যাতে না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সবাইকে তার চিন্তা প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।
১৬. অর্থের প্রাচুর্য: অর্থ সংগঠনের অত্যন্ত প্রয়োজন। অর্থ ছাড়া সংগঠনের অগ্রগতি কঠিন। কিন্তু অর্থ যদি আবার বেশি হয়ে যায়, অর্থের প্রাচুর্য দেখা দেয় তাহলে তার ফলাফল শুভ নয়। অর্থের প্রাচুর্যের ফলে নানা সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেয় যা সাংগঠনিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
১৭. সময় নিষ্ঠার অভাব: একটি সংগঠনকে তার সমস্ত কাজ-কর্ম যথাসময়ে সম্পাদন করতে হবে। যথাসময়ে সভা-বৈঠকাদি শুরু করা থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যন্ত সর্ব ক্ষেত্রেই সময়ের মূল্য দেওয়া উচিত। তাহলে পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ থাকবে। আর যদি সময়ের গুরুত্ব না দেয়া হয় তাহলে তার ফলাফলস্বরূপ পরিবেশও ক্ষুণ্ণ হতে থাকবে।
১৮. দায়িত্বশীলদের নিষ্ক্রিয়তা: দায়িত্বশীলগণের সক্রিয়তা ও ভূমিকার উপর সংগঠনের অগ্রগতি প্রধানত নির্ভরশীল। দায়িত্বশীলগণ যদি তাদের দায়িত্ব কাম্য মানে পালন না করেন, তাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা ও শিথিলতা দেখা দেয় তাহলে ধীরে ধীরে প্রশ্ন, ক্ষোভ ও অভিযোগ ধুমায়িত হয়ে ওঠে। ফলে সাংগঠনিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।
মোটকথা বিভিন্ন কার্যকারণেই সাংগঠনিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, নষ্ট হতে পারে। তাই সামষ্টিকভাবে সবাইকে এসব বিষয়ের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। পরিবেশ বিনষ্টকারী সমস্ত আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে।
যা পরিবেশ সুন্দর করে
এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা সাংগঠনিক পরিবেশকে সুন্দর করে, সুস্থ করে। যেমন
১. চিন্তার ঐক্য: চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি করা গেলে সাংগঠনিক পরিবেশ সুন্দর হয়।
২. সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা: সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তার উপর দৃঢ়তা অবলম্বন পরিবেশের জন্য ইতিবাচক। ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করে, পরিবেশ নষ্ট করে।
৩. অধিকাংশ মতের প্রতিফলন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মতের প্রতিফলন ঘটলে পরিবেশ সংরক্ষণে তা হবে অনুকূল।
৪. যথাযথ বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে পরিবেশ ভাল থাকে।
৫. মতপার্থক্যের সুযোগ থাকা: সংগঠনের ভেতরে নিয়মানুগ পন্থায় মত-পার্থক্যের সুযোগ থাকলে পরিবেশ সুস্থ থাকে।
৬. পারস্পরিক সমস্যা ও অবস্থার অবগতি: পারস্পরিক সমস্যা সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে অনেক ভুল পদক্ষেপ, ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়, সঠিক কর্মবণ্টন হয় না। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একে অন্যকে ভাল করে জানা প্রয়োজন। একে অন্যের সমস্যা বোঝা প্রয়োজন।
৭. সংশোধনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়া: কাউকে সংশোধন, কারো ভুল-ত্রুটি দূর করার ক্ষেত্রে যদি বিজ্ঞতা ও সতর্কতার পরিচয় দেয়া হয় তাহলে পরিবেশ ভাল থাকে। সংশোধন কার্য একটি কঠিন ও জটিল কাজ। এক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিপরীত ফল হতে পারে। তাই সতর্কতা ও বিজ্ঞতা অবলম্বন প্রয়োজন।
৮. যোগ্যতার মূল্য দেয়া, গুণের কদর করা: সংগঠনের ভেতরে যোগ্যতার মূল্য দিলে, গুণের কদর করলে পরিবেশ সংরক্ষণে তা হবে সহায়ক।
৯. আচরণের সমতা বিধান: পরিবেশের জন্য আচরণের ক্ষেত্রে সমতা বিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচরণে বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব পরিবেশকে নষ্ট করে।
১০. মৌলিক বিষয়ের উপর বেশি জোর দেয়া: পরিবেশ ভাল রাখতে হলে ও মৌলিক বিষয়ের উপর বেশি জোর দিতে হবে। খুঁটিনাটি বিষয়ে বাড়াবাড়ি পরিহার করতে হবে। ছোটখাট বিষয়ে সংশোধনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ও হেকমত অবলম্বন করতে হবে।
১১. নেতৃত্বের প্রতি সুগভীর আস্থা: সংগঠনের কাম্য পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণে নেতৃত্বের প্রতি কর্মীদের সুগভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে আস্থা ও শ্রদ্ধার অভাব থাকে সেখানে পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হবেই। আবার যেখানে শ্রদ্ধা ও আস্থা আছে সেখানে সুন্দর ও ভাল পরিবেশ বিরাজ করবে।
বস্তুত প্রতিটি ভাল আচরণ, পদক্ষেপ ও গুণই সাংগঠনিক পরিবেশকে উন্নত করবে। তাই ভাল গুণের চর্চা বৃদ্ধি করা দরকার।
পরিবেশ উন্নত করার জন্য করণীয়
পরিবেশকে উন্নত করতে হলে, কাম্য মানে পৌঁছাতে হলে কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে।
১. ১ . কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত গুণাবলী অর্জন: সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী বাহিনীকে কুরআন-সুন্নাহর বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করার জন্য এবং দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর যথাযথ ও ব্যাপক চর্চা বাড়াতে হবে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে কুরআন-সুন্নাহ কেন্দ্রিক আমলের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে।
২. সমস্ত কাজ যথানিয়মে করতে হবে: গঠনতন্ত্র ও গৃহীত নিয়ম পদ্ধতিতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ-কর্ম সম্পাদন করতে হবে। অনিয়মে কোন কিছু করা, বলা বা আচরণের প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।
৩. যথার্থ এহতেসাবের অনুশীলন: এহতেসাব যেহেতু সংগঠনের পরিবেশ সংরক্ষণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাই এহতেসাবের অনুশীলনের উপর জোর দিতে হবে।
৪. সমস্যা দেখা দিলে তার তড়িৎ সমাধান: সংগঠনের ভেতরে নানা কারণে সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিতে পারে। সমস্যা সৃষ্টি হলে অতি দ্রুত তা নিরসনের পদক্ষেপ নিতে হবে। বিলম্ব পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।
সংগঠনের মজবুতি অর্জন
একটি সংগঠন গড়ে তুললেই হবে না, সংগঠনের মজবুতিও অর্জন করতে হবে। মজবুত ও শক্তিশালী সংগঠন ছাড়া লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। একটি মজবুত সংগঠনের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো প্রধানত-
১. যোগ্য ও সঠিক নেতৃত্ব: যোগ্য ও সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠনের মজবুতি অর্জন দুরূহ ব্যাপার। নেতৃত্ব যত মজবুত হয় সংগঠন তত মজবুত ও শক্তিশালী হবে।
২. মানসম্পন্ন কর্মী-সদস্য: একটি সংগঠন শুধু কিছু যোগ্য নেতৃত্বের মজবুতি লাভ করে না; বরং সংগঠনের কর্মী বাহিনীল মানের উপর মজবুতি অনেকটা নির্ভর করে। যে সংগঠনে আন্দোলনের দাবি অনুযায়ী মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত কর্মী বাহিনী রয়েছে সে সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই মজবুত হয়। তাই মজবুতি অর্জনের জন্য কর্মীদের মান উন্নত করতে হবে।
৩. নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রম: একটি সংগঠন তখনই মজবুত হতে পারে যখন সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রমগুলো নিয়মিত ও যথানিয়মে সম্পাদিত হয়। একটি সংগঠনের যে সমস্ত কাজ নিয়মিতভাবে করতে হয়। যেমন বৈঠকাদি অনুষ্ঠা, পরিকল্পনা গ্রহণ, কাজের রিপোর্টিং, সর্বস্তরে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, দাওয়াতী তৎপরতা, বায়তুল মাল সংগ্রহ ইত্যাদি। যদি নিয়মিত বা রুটিন কাজ নিয়মিত না হয় তাহলে সে সংগঠনকে শক্তিশালী সংগঠন বলা যাবে না। নিয়মিত কাজগুলো নিয়মিত হওয়াই মজবুতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। তাই কোন সংগঠনকে মজবুত ও শক্তিশালী করতে হলে প্রাত্যহিক ও নিয়মিত কাজগুলো নিয়মিতই করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
৪. সঠিক সম্পর্ক ও পরিবেশ: একটি সংগঠন মজবুতি অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও পরিবেশ কাম্য মানের হওয়া চাই। কর্মীদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, টীম স্পিরিট, শূরায়ী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অভ্যন্তরীণ ইনসাফ, এহতেসাব উদ্ভূত সমস্যার দ্রুত সমাধান, সর্বস্তরে সুষ্ঠু যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও পরিবেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোন সংগঠনে যদি উল্লেখিত বিষয়গুলোর অভাব থাকে বা কাম্য মানের অনেক নিচে অবস্থান করে তবে সে সংগঠন মজবুতি লাভ করতে পারে না। তাই সংগঠনকে মজবুত করতে হলে এসব বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। পরিবেশ ও সম্পর্কের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে হবে।
৫. মজবুত বায়তুল মাল: একটি সংগঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে তার মজবুত বায়তুল মাল। আন্দোলন ও সংগঠন চালাতে অর্থ প্রয়োজন হয়। তাই ন্যূনতম অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকলে অনেক কর্মসূচিই বাস্তবায়িত করা যায় না। এজন্য আর্থিক শক্তিও সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন। সংগঠন শক্তিশালী হলে বায়তুল মালও মজবুত হয়। আবার বায়তুল মাল মজবুত করতে পারলে সংগঠনকে মজবুত করা সহজ হয়। মনে রাখা দরকার বায়তুল মাল নিয়মিত হওয়া চাই। অনিয়মিত অর্থসংস্থানের মাধ্যমে সংগঠনের মজবুতি আসে না। এজন্য অন্যান্য উপাদানও ঠিকমত থাকা চাই এবং অর্থের যথাযথ ব্যবহারও নিশ্চিত করা চাই।
মোটকথা মজবুত বায়তুল মাল প্রয়োজন। মজবুত বায়তুল মালের জন্য নেতা ও কর্মীদের নিয়মিত আর্থিক ত্যাগ-তিতিক্ষাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তৎসঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষী-শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধি, সংগঠনের প্রভাব বলয় বাড়ানো এবং তাদের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে বায়তুল মাল মজবুত করা যেতে পারে। তদুপরি আন্দোলন যত গণমুখী হবে, জনসমর্থন যত বাড়বে ততই বায়তুল মালের আয় বৃদ্ধি পাবে। তাই বায়তুল মাল মজবুত করার জন্য আমাদেরকে সর্বস্তরে আর্থিক ত্যাগের মনোভাব ও অভ্যাস সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির পরিকল্পিত প্রয়াস চালাতে হবে।
৬. প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সংহতি: একটি সংগঠন তখনই সত্যিকার অর্থে মজবুত বলে পরিগণিত হতে পারে যখন অভ্যন্তরীণ ও বহিচাপের সফল মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। একটি সংগঠনকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে অনেক সময় নানা সমস্যা ও চাপের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় সংগঠনে সংহতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। নানা ধরনের মতবিরোধ ও কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সংগঠনের ভেতরে আন্দোলনের স্বার্থবিরোধী কারো অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। এসব পরিস্থিতিতে যদি সংগঠন দৃঢ় থাকতে পারে, পরিস্থিতির সফল মোকাবেলা করতে পারে, সংগঠনকে সংহত রাখতে পারে তাহলে তাকে মজবুত সংগঠন বলা চলে। আর যদি সামান্য অভ্যন্তরীণ সঙ্কট সৃষ্টি হয়ে সংগঠন নড়বড়ে হয়ে যায়, কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও বিভ্রান্তি দেখা দেয়, কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তাকে মজবুত সংগঠন বলা চলে না।
সংগঠন বাইরের থেকেও নানা চাপ ও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। সংগঠনের উপর বা নেতৃত্বের উপর সরকারি জুলুম-নির্যাতন নেমে আসতে পারে। বিরোধী পক্ষ থেকেও সংগঠন আক্রান্ত হতে পারে। সংগঠনের বিরুদ্ধে নানা প্রচারণার সয়লাব বয়ে যেতে পারে। এসব পরিস্থিতি যদি সংগঠন সামলে নিতে পারে তাহলে তা অবশ্যই তার মজবুতির প্রমাণ। আর যদি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংগঠন সক্ষম না হয় তাহলে এটা দুর্বলতার লক্ষণ।
মোটকথা অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সমস্যা এবং সঙ্কট মোকাবেলায় যদি সংগঠন সক্ষম হয় তাহলে এটা শক্তি ও মজবুতির লক্ষণ। তাই মজবুত ও শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হলে ভেতর-বাইরে যে কোন সমস্যা সঙ্কটের মোকাবেলার মত সামর্থ্য ও প্রস্তুতি থাকতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে চিন্তার ঐক্য, পর্যাপ্ত সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, নিষ্ঠা, সতর্কতা, সদা প্রস্তুতি, আনুগত্য, যথাযথ কর্মসূচি, নেতৃত্বের সাহসিকতা, নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনীর আখেরাতমুখীতা ইত্যাদি।
৭. স্থিতিশীলতা ও কাজের সিস্টেম গড়ে তোলা: সংগঠনের মজবুতির জন্য স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। হঠাৎ করে আলোড়ন সৃষ্টি করে আবার নেতিয়ে পড়লে তা সংগঠনের দুর্বলতার লক্ষণ। মজবুত সংগঠনের কাজে ও তৎপরতায় ধারাবাহিকতা এবং স্থিতিশীলতা থাকে বলেই কাজের একটি সিস্টেম গড়ে ওঠে। কোন বিশেষ ব্যক্তি নির্ভর যে কাজ, যা ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে স্তিমিত হয়ে যায় তা কখনো মজবুত সংগঠনের বৈশিষ্ট্য নয়। ব্যক্তির পরিবর্তন হলেও যদি কাজের ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে তাহলে সংগঠন মজবুত হবে। যেখানে কাজের স্থায়িত্ব নেই, কাজের কোন নিয়মিত সিস্টেম গড়ে ওঠেনি, যেখানে কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয় না সেখানে সংগঠনের দুর্বলতা খুবই স্পষ্ট। তাই মজবুত সংগঠন গড়ে তুলতে হলে কাজের সিস্টেমের উপর জোর দিতে হবে। সংগঠন যাতে স্থিতিশীল হয়, স্থায়িত্ব লাভ করে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। মৌসুমী তৎপরতা, ব্যক্তি-নির্ভর তৎপরতার চেয়ে ধারাবাহিক ও সিস্টেম নির্ভর তৎপরতা বেশি প্রয়োজন। তাহলেই মজবুত সংগঠন গড়ে উঠবে।
৮. ধারণা ক্ষমতা ও গতিশীলতা: একটি মজবুত সংগঠনের জন্য সংগঠনের ধারণ ক্ষমতা ব্যাপক হওয়া চাই। সমাজের বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার ক্ষমতা সংগঠনের থাকতে হবে। সংগঠন যদি বিভিন্নমুখী হয় অথবা আকৃষ্ট করলেও ধরে রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে সে সংগঠন যথার্থ অর্থে মজবুত বলা চলে না। তাছাড়া সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে যদি গতিশীলতা না থাকে তাহলে এক সময় সংগঠন স্থবির হয়ে পড়তে পারে। কখনও কখনও বিশেষ ধরনের লোকদের বা বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়তে পারে। এমনটি হলে সংগঠনের গতি থেমে যাবে, তার ব্যাপকতা রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে সংগঠন একটি গতানুগতিকতায় পরিণত হবে। ফলে সংগঠনের পক্ষে তার লক্ষ্যে পৌঁছানো দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সংগঠনের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ও ব্যাপকতা-গতিশীলতা সৃষ্টি প্রয়োজন। আর এর জন্য নেতৃত্বের উদারতা, পরিচালনা, কর্মসূচি, কাজের সৃজনশীলতা, চিন্তা বিকাশের সুযোগ, যোগ্য লোকদের যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত করা, কোন বিশেষ গ্রুপের প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ না থাকা, আন্তরিকতা ও যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন ইত্যাদি সবিশেষ প্রয়োজন।
উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সামনে রেখে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে আন্তরিক প্রয়াস চালালে আশা করা যায় ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার উপযোগী একটি মজবুত ও আদর্শ সংগঠন গড়ে তোলা যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!
সমাপ্ত